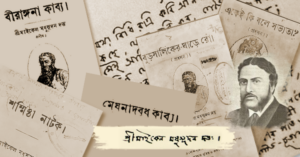এই ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সারা দেশেই অমৃত মহোৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। অথবা, জাতীয় জীবনে, রাজ্যস্তরে, গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু ঘটছে, তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে চলেছে অমৃত মহোৎসবের নাম। দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে চলার জন্য সামরিক প্রস্তুতি আমাদের আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাবার পরিবেশও এখন পৃথিবীতে নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে উপনিবেশ তৈরির প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন এসেছে। বিনিয়োগের আন্তর্জাতিক চলাচল এখন সামরিক নিয়ন্ত্রণের জায়গা নিয়েছে। আমাদের কৃতিত্ব কিন্তু কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ৭৫ বছর ধরে রক্ষা করতে পারার মধ্যে নয়। ভারত এই স্বাধীনতাকে এ-যাবৎ লালন করেছে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে। বিপুল বিস্তার, বহু বৈচিত্র্যের একটি দেশে এ কোনও সহজ কথা নয়। একজন লেখক হিসেবে এই স্বাধীন গণতন্ত্রে জীবনযাপন এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। এই জীবনযাপন কিন্তু কেবল আমার একার নয়। নিজস্ব জীবনযাপনে লেখক একক ব্যক্তি নন, যাদের জীবন নিয়ে তাঁর চর্চা, সেই জনসমাজের সম্মিলিত উপস্থিতি ঘটে সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে।
আমার লেখালিখির আরম্ভ সেই কিশোরীবেলায়। তখন দেশের স্বাধীনতারও যৌবনকাল। বাবা-মায়ের দেশ ছিল খুলনা জেলায়। তখনকার পুব বাংলায়। ১৫ অগাস্টের পর আরও তিন মাস খুলনা জেলা ভারতের অংশ হয়ে রয়ে গিয়েছিল। কোন জেলা কোনদিকে পড়বে, তাই নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। তারপর পিতামহ-পিতামহী চলে এসেছিলেন ভিটেমাটি, জমি-জিরেত ছেড়ে। এইটুকুই রক্ষা, কলকাতায় একটা পা রাখার জায়গা ছিল, বাবার চাকরির সূত্রে। কালীঘাটের কাছে একটা ভাড়াবাড়ি। নাহলে রিফিউজি ক্যাম্পেই সকলকে জীবন আরম্ভ করতে হত। সে হত এক অন্যরকম জীবন। শৈশবে তাই স্বাধীনতাকে ছাপিয়ে মনের মধ্যে থাকত দেশভাগের অনুষঙ্গ। বাবা-মা যে পুকুর, স্থলপদ্মের গাছ, ক্ষেতের আল ধরে হাঁটার স্মৃতি চিরতরে ত্যাগ করে এসে এত কষ্ট পাচ্ছেন, সেই না-দেখা দেশের জন্য মনকেমন করা লেগে থাকত। সেইজন্য ভারত তখনও আমার আপন হয়নি। এক অলীক কল্পনা আমার মধ্যে কাজ করত। একদিন দুই বাংলা এক হয়ে যাবে আর আমি ইচ্ছেমতন ফেলে আসা দেশে আসা-যাওয়া করব। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখন আমিও বাস্তবে পা রাখলাম। সেদিন বাঙালি হিসেবে গর্ব অনুভব করলাম আর নিজের দেশ ভারতকেও আপন করে নিতে পারলাম।
কবিতা দিয়েই আমার লেখক-জীবন আরম্ভ। সেই পর্বে অন্য কিছু লেখার কথা তখনও আমার কল্পনাতেই ছিল না। কবিতা ও জীবন বিষয়ক গদ্য অল্পস্বল্প লিখেছি। কিন্তু কাজের জীবন শুরু করতে গিয়ে আমাকে যখন কলকাতা ছাড়তে হল, আমার চেতনায় ভারতবর্ষ ঝেঁপে এল দুর্দান্ত মেঘবৃষ্টির মতো। অন্যমনস্ক কবি থেকে সচেতন গদ্যকারে রূপান্তরিত হবার সময় এল। এত প্রিয় আমার যে কলকাতার নীড়, তা ছাড়ব আগে কখনও ভাবিনি। অথচ সেই দিনগুলিতে কলকাতার দৈনন্দিনতা আমার চেতনায় নিগড়ের মতো চেপে বসছিল। নিষ্ক্রমণকেই তখন মনে হচ্ছিল একমাত্র পথ। গদ্যকার জীবনপর্বের সূচনায় আমি বাংলার বাইরে। ভাষার পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যেমন একদিকে দিশেহারা বোধ করছি, অন্য দিকে বহু ভাষা, অনেক স্বর ও ভিন্ন সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের এক পৃথিবীর আকর্ষণ আমার কাছে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমার কাজ আমাকে নানা ভাবে মানুষের জীবন ও জীবিকা বুঝতে শেখায়। গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে মানুষের কাছে গিয়ে দেখলাম, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে জীবনের সুযোগ-সুবিধে। যাঁরা চাষের জল পেলেন, একফসলি জমি দোফসল হল, তাঁরা পেলেন পছন্দমতো বাঁচার পথ। বড় বাঁধের জন্য যাঁদের ভিটেমাটি গেল, চাষের জমি গেল, তাঁরা ছিন্নমূল হয়ে কে কোথায় গেলেন!

যাঁদের কন্ঠস্বর হারিয়ে গেল, তাঁদের স্বাধীনতাও খণ্ডিত হল। উন্নয়নের পরিণাম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন রকম। গ্রাম ও শহরে উন্নয়নের প্রভাব আলাদা। দেশের ভিতর মানুষের চলাচল চলেছে নিরন্তর। গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে মানুষ আসছে। দেশান্তরী হয়ে অন্য রাজ্যে চলেছে দিনমজুর ও প্রান্তিক চাষি। সাহিত্যের মধ্যে যাঁরা জীবনকে দেখেন, তাঁদের সন্ধান থাকে এই প্রবহমানতার। আসলে দেশটা যে একটা ‘হোমোজিনাস মনোলিথ’ নয়, তার মধ্যে আছে নানা স্তর ও মাত্রা, নিরুপায় মানুষের জীবনযুদ্ধের নানান অসংগতি, এই বোধই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন। প্রেমচন্দ থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী, রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভূতিভূষণ, ভারতীয়ত্বর এই অশ্রুত স্বরের লিপিকার হয়ে স্মরণীয় হয়েছেন। আমার সাহিত্যের উত্তরাধিকার এঁদের কাছেই পাওয়া।
স্বাধীনতার স্বপ্ন, বিভিন্ন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কাছে স্বতন্ত্র। কারণ এঁদের ইতিহাস আলাদা। অস্তিত্বের সংগ্রাম আলাদা রকমের। ইতিহাসও গড়ে ওঠে নানা ভাবে। ছাপা বইতে যে-ইতিহাসের বৃত্তান্ত আমরা পড়ি, তাতে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজন্যবর্গের কথাই লিপিবদ্ধ হয়। কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাস কিংবা সেখানকার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস আমাদের পাঠকের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা প্রকৃতিগত ভাবে আলাদাও। কারণ সেই ইতিহাসে মিশে থাকে মিথ, কিংবদন্তি, বহু প্রজন্ম ধরে শুনে আসা গল্পকাহিনি, বীরগাথা। সেই সব ইতিহাসের সন্ধানে বেরোলে তবেই এদের স্বাধীনতার পরিভাষা বা স্বপ্নকে বোঝা সম্ভব হবে। যেমন, যে মহাভারত-রামায়ণ আমরা ছাপা অক্ষরে পড়ি, তার অসংখ্য প্রকারভেদ আছে নানা জনজাতির মৌখিক ইতিহাসে। এগুলি সংগ্রহ করা বা শোনা একজন লেখকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় পড়েছি, তাঁর মুখেও শুনেছি যে, সাহিত্য রচনায় বাস্তব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ মিথ এবং মৌখিক ইতিহাস। এগুলি আমাদের মাটির কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে। আদিবাসীবহুল অঞ্চলে গিয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলির প্রান্তিক অবস্থান দেখে আমি বারবার বিষণ্ণ হয়েছি। কেন এমন হল? স্বাধীনতা আন্দোলনে মৃত্তিকার এই সন্তানরা আমাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন। অথচ তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাল করে বোঝার জন্য যে অধ্যবসায় প্রয়োজন ছিল, তা আমাদের স্বাধীন দেশের রাজনীতিক ও প্রশাসকরা দিতে পারেননি। আমরা উন্নয়নকে দেশের লক্ষ্য বলে মেনেছি, কিন্তু তার মধ্যে যে নানা ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণির প্রয়োজনকে সম্মিলিত করতে হবে, সেই দূরদৃষ্টি আমাদের নীতি-প্রণেতাদের ছিল না। যারা অরণ্যের উপর নির্ভরশীল, তাদের দৈনিক প্রয়োজনের জন্য মধু, ওষধি, ঘাস, বাঁশ, মহুল ইত্যাদি নানা জিনিস, তাদের সঙ্গে অরণ্যের সম্পর্ক আমরা ক্রমশ সীমায়িত করে এনেছি আমাদের অরণ্য সংরক্ষণ নীতির বলে। ধীরে ধীরে যারা এ-ভূমির অধিপতি ছিল, তারা পরিণত হয়েছে ভূমিহীন অধিকারহীন, কণ্ঠস্বরহীন ছায়ামানুষে। স্বাধীনতার পর যখন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন হল, তৈরি হল স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র, বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি বিভক্ত হয়ে গেল নানা রাজ্যে। ভীলরা ভাগ হয়ে গেল মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশে। গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড বা সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ— এর যারা মূল অধিবাসী, সেই গোণ্ডরা ছড়িয়ে গেল মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের নানা জেলায়। গোষ্ঠীজীবনের সংহতি ও অন্বয় নষ্ট হয়ে তারা পরিণত হল বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীতে।

ভারতের মতো এক গণতন্ত্রে যদি আমরা কেবল গণতন্ত্রের বিস্তারের কথা না ভেবে তাকে গভীরতর স্তরে পৌঁছে দেবার কথাকে অগ্রাধিকার দিই, তাহলে ভোটাধিকারের বাইরের পরিসরেও মানুষের জীবিকার, আত্মপ্রকাশের, মানবাধিকারের কথা ভাবতে হবে। আদিবাসী, দলিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক যাঁরা কাজের সন্ধানে নিজের এলাকা বা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে অন্যত্র গ্রামে আছেন এবং শহরেও, তাঁরা আমাদের জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি। কোনও শিল্প-সাহিত্যের কর্মী এঁদের জীবনকে বাদ দিয়ে যদি সৎ সাহিত্য রচনা করতে চান, তাহলে তা হবে বাস্তব থেকে খিড়কি দরজা দিয়ে পালানোর সমান। কিন্তু এ তো সাহিত্যিকের নিজস্ব অভিরুচি। তিনি যদি আগ্রহী না হন জনজীবনের রাজনীতি-অর্থনীতিতে, তবে কার কী বলার থাকে! এখানেই আমাদের মতো দেশের সাহিত্যকারদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ, নিজেকে অতিক্রম করে সমাজের সঙ্গে মানুষের অন্বয়কে অনুসন্ধান করা। তার জন্য ঘর ও অভ্যস্ত বৃত্ত ছেড়ে নিজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমরা যদি ইতিহাসের আঞ্চলিকতায় বিশ্বাস না করি, তা পু্নর্লিখনের জন্য উদ্যোগী না হই, একটি স্বাধীন দেশের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না।
স্বাধীনতার একটি অন্যতম মাত্রা— মুখের ভাষা, লিপি। সংবিধানে ২২টি স্বীকৃত ভাষার বাইরেও ভারতের মানুষ ৭৮০টি ভাষা বলে। ভাষাবিদ গণেশ দেভি বিশেষজ্ঞ ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। পিপল্স লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া। একটি বড় স্বেচ্ছাসেবী দল এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যোগ দিয়েছিল তাতে। ১৯৬১ সালের জনগণনায় মাতৃভাষা পাওয়া গিয়েছিল ১৬৫২টি। ১৯৭১-এ তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১০৮-এ। ১০৯ নম্বরে ছিল— বাকি অন্য সব। গণেশ দেভির ভাষা গণনায় জনজাতি ও যাযাবর গোষ্ঠীর বলা ৪৮০টি ভাষা পাওয়া গিয়েছিল। নানা ভাষা। লিপিযুক্ত, লিপিহীন। জনজাতি গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা ঘরে বাবা-মায়ের সঙ্গে যে-ভাষা বলে, স্কুলে তা না বলার ফলে ভাষাগত দক্ষতা হারাচ্ছে। এছাড়া হারিয়ে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে বহু ভাষা। তার সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে সেই ভাষায় লেখা গান, কাহিনি, আখ্যান, স্থানিক ইতিহাস। বলা যায় ঝরে ঝরে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে আমাদের সময়। আমরা লেখকরা ছাড়া তাকে পুনরুদ্ধার করবে কে!
৭৫ বছর একটি রাষ্ট্রর জীবনে খুব সময় নয়। স্বাধীনতার পর ভারী শিল্পে বিনিয়োগের নীতি থেকে আমরা গেছি দারিদ্র দূরীকরণ ও কৃষির উন্নয়নে। উনিশশো আশির দশকে বাংলা ও কেরালায় বর্গাচাষ নথিভুক্ত হয়েছে, সিলিং জমি বন্টন ও হস্তান্তর করা হয়েছে ভূমিহীনদের। এই পর্বে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে উতরোল ঘটল, তার প্রতিধ্বনি আমাদের সাহিত্যেও ঘটেছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যে গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষিতে মালিক-কৃষক সম্পর্কের বদল নিয়ে লেখা হয়েছে গল্প-উপন্যাস। উনিশশো নব্বই-এর গোড়ায় সংবিধান সংশোধন করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি হল। গণতন্ত্র গভীরে শিকড় ছড়াতে পারল, কিছুটা হলেও। যেসব রাজ্যে গ্রামসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ জনসমর্থন নিয়ে কাজ করতে পেরেছে, সেখানেই রাজনীতির ক্ষমতা-কেন্দ্রিকতা কিছুটা হলেও পিছনে হটেছে। এর সমান্তরাল ভাবেই উনিশশো নব্বই-এর দশকে উদার অর্থনীতির বিকাশ হতে লাগল। বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ল, সুদের হার কমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু একই সঙ্গে এর অভিঘাতে বদলে গেল বৈষম্যের আকার-প্রকার। গ্রামের কৃষিজমির উপর নজর পড়ল শিল্পের, বদলে গেল শহরের নকশা এবং ক্রেতাদের ভোগ্যপণ্য নির্বাচনে অগাধ অধিকার দিতে গিয়ে তৈরি হল এক সুবিধাভোগী মধ্যস্বত্ব শ্রেণী। আমরা গ্রাম-শহরের লেখকরা বিশ্বায়নকে নানা দিক থেকে দেখেছি। তার নানা ভাষ্য উঠে এসেছে আমাদের সাহিত্যে।

স্বাধীনতাকে কেবল ১৯৪৭-এর অর্জন মনে করলে চলবে না। দেশ স্বাধীন। তার নাগরিক স্বাধীন। কিন্তু লেখকের জন্য স্বাধীনতা হোক প্রতিদিনের অনুভব। কেবল তাহলেই আমরা বুঝব প্রান্তিক ও ক্ষমতাহীন মানুষ কেমন আছেন। গত দু’দশকে দেশে প্রাচুর্য বেড়েছে, ক্রেতার স্বাধীনতা বেড়েছে। বড় বড় বিপণি ভরে উঠেছে পণ্যে। শতাংশের হিসেবে দারিদ্র কমেছে। কিন্তু বেড়েছে ভূমিহীনের সংখ্যা। বেশি মজুরির খোঁজে যাঁরা জেলা বা রাজ্যের বাইরে যাচ্ছেন, তাঁদের জীবনে কী বিপুল অনিশ্চয়তা কেবল দু’বেলা খাওয়া, মাথার উপর ছাদ নিয়ে, এই অতিমারীর সময়ে আমরা দেখলাম। আদিবাসীর জমি ও জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শিল্পের আগ্রাসন থেমে নেই। নিজের জীবিকা, মানবাধিকার নিয়ে মানুষকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে প্রত্যহ। অতিমারীকালেই সংশোধিত হয়েছে শ্রম আইন, পাস হয়েছে কৃষি বিল। মানুষ গৃহবন্দি, বিচ্ছিন্ন, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য, অক্সিজেনের জন্য হাহাকার। রাষ্ট্রযন্ত্র কিন্তু থেমে নেই। তার নিঃশব্দ, বিমর্ষহীন পদসঞ্চার চলেছে। সাহিত্যর কাজ এই আলো-অন্ধকার কালে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তা আমরা অনেকেই পারিনি, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কলম চলেছে ঘরের কোণায়। লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নিজেদের জীবনকে স্পর্শহীন, সুরক্ষিত রাখার চেষ্টায় আমরা অনেকেই মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি।

গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের জীবনে স্বাধীনতার অনুভবকে উজ্জীবিত রাখে নানা অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে। তেভাগা থেকে নকশালবাড়ির আদিবাসী কৃষক আন্দোলন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন বিল থেকে কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন, এ সবই ভারতীয় গণতন্ত্রের অলংকার। সার্বভৌমত্ব অর্জন করার পরও মানুষের প্রত্যাশা থাকে, অধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ কোনও লজ্জার কথা নয়, বরং গণতন্ত্রের সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এর অর্থ মানুষ একটি সজীব প্রাণবন্ত ব্যবস্থার সঙ্গে বার্তালাপ করছে, কোনও কাঠ-পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে নয়। স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে গেলে নানা গণ আন্দোলনের ইতিহাস আনতেই হবে সাহিত্যে। কারণ এগুলি এক মুক্ত দেশের নাগরিকদের গভীরতর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।
আমার সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘মহাকান্তার’ লিখতে গিয়ে দু’বছর আগে আমি আবার গেলাম সেই প্রাচীন ভূমিতে, ইন্দ্রাবতী নদীর সঞ্চার-পথ অনুসরণ করে, মধ্য ও দক্ষিণ ওড়িশার অরণ্য-পর্বতসংকুল জমি অতিক্রম করে ছত্তিশগড়ের দুর্গমতা পার হয়ে শেষে গড়চিরোলি। গড়চিরোলিতে ইন্দ্রাবতী নদী মিশেছে গোদাবরীতে।

এই পথের অনেকটাই আজ ‘রেড করিডর’ নামে পরিচিত, এর দুই পাশে একদা ছিল সেই প্রাচীন অরণ্য। পদ্মপুরাণের সেই ‘মহাকান্তার’ দণ্ডকারণ্য নামেও চিহ্নিত হয়। প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণের মূল্য দিতে গিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়েছে গোণ্ড, কন্ধদের মতো জনজাতি গোষ্ঠী। নিয়মগিরির আদিবাসী ‘নিয়মরাজার দেশ’কেই মনে করে তার ভারতবর্ষ। তাদের কাছে দেশের অন্য সংজ্ঞা নেই। কিন্তু সেই ‘রাজার বাড়ি’কে বক্সাইট খননের হাত থেকে রক্ষা করতে স্বাধীন দেশের সরকারের সঙ্গে তাদের লড়াই করতে হয়। অন্যদিকে আজ থেকে দেড় দশক আগেও ‘সালওয়া জুড়ুম’-এর মতো পরিকল্পিত এক অভিযান জনজাতি সমাজের অস্তিত্ব ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। মাওবাদী দমনের নামে আদিবাসী গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল ক্যাম্পে, ফিরে এসে দেখে হাতবদল হয়ে গেছে তাদের ভিটেমাটি, চাষজমি।

যত দিন যায়, কর্পোরেট পুঁজি প্রভাবিত করে উন্নয়নকে। রাষ্ট্রের জনমুখী অভিনিবেশ বদলায়। সীমান্ত প্রহরার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, কারণ নাগরিকের সুরক্ষার নামে সামরিক ব্যয়ের বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অনুপ্রবেশ হয়ে ওঠে দেশের জন্য বিপজ্জনক। তখন আবার নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় এসে পড়ে যাদের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তাদেরই উপর। দেশের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাই দেশদ্রোহের যে-কোনও আভাস হয়ে পড়ে চিন্তাজনক। স্বাধীনতার ৭৫ বছরের উৎসবে তাই নাগরিক আন্দোলনের নানা প্রবাহ স্বাভাবিক ভাবে এসে মেশে। অতিমারীর আগেই দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার আন্দোলন। আজ এক বছর হল কৃষকদের এক বড় অংশ পথে বসে আছেন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে। কিন্তু তাদের কথা শোনার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই নিজেরাই সংসদ বানিয়ে তাঁরা কৃষি আইনের আলোচনা করে চলেছেন। ভীমা কোরেগাঁও মামলার সর্বশেষ অভিযুক্ত নব্বই বছর বয়সি স্ট্যান স্বামী জেল হেফাজতেই মারা গেলেন। বিচারধীন বন্দির অধিকার হিসেবে জামিন চেয়েছিলেন। তা জীবৎকালে পাননি তিনি। রাষ্ট্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কিন্তু তাঁর কাস্টডি চায়নি, অপরাধের নথি পেশ করেনি। অথচ জামিনও দেয়নি। বিচারব্যবস্থার অন্তর্নিহিত এই পরস্পর বিরোধিতা আমাদের ভাবায়। তবে কি জনজাতির অধিকারের জন্য আন্দোলন, যে-কাজটি স্ট্যান স্বামী আজীবন করে এসেছেন, তা রাষ্ট্রব্যবস্থার পছন্দ ছিল না? এই অপছন্দের ফল কি চরম দণ্ড? ভারতের সংবিধান আমাদের দিয়েছে এই প্রশ্নগুলি লেখার পরিধিতে আনার স্বাধীনতা। জীবনের সঙ্গে সৃজনশীলতার অন্বয় তাই স্বাধীন দেশের একজন লেখকের জন্য অমৃত মহোৎসবের উদযাপন।
ছবি সৌজন্যে: লেখক