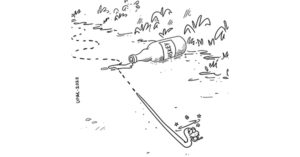রমিতা (তিন)
চম্পতিমুন্ডা পর্ব শেষ করে, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে রণেন ফিরে এল সোদপুরের বাড়িতেই। তরুলতা আবারও হাল ধরলেন সংসারের। ভূতেশের পরিবারের সঙ্গেও কিছুটা হলেও যে সহজ হয়ে এসেছে সম্পর্কের আদান-প্রদান, তার অন্যতম কারণ হল, তরুলতাকে লেখা ভূতেশের এই চিঠিটি।
পূজনীয়া বেয়ান, ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৯ – সোদপুর
দিল্লি থাকাকালীন, তনুদার চলে যাবার খবর সেখানে পেয়েও আপনাকে কোনও পত্রাদি পাঠাইনি। আমার এই অনুচিত ঔদ্ধত্য প্রকাশেরর জন্য দেরিতে হলেও, আপনার কাছে সবিশেষ মার্জনা চেয়ে সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর এই চলে যাওয়া শুধু যে আপনার পরিবারের পক্ষেই এক সমূহ বিপর্যয় তাই নয়, এ-ক্ষতি আমারও। কতভাবে যে তাঁর কাছে আমি ঋণী, সে-কথা মুখে বলে বা বিস্তারিতভাবে লিখে প্রকাশ করেও তা বোধহয় বোঝাতে পারব না। তনুদার মতো সুযোগ্য এক ন্যায়পরায়ণ এবং দায়িত্ববান মানুষ এ-সংসারে প্রায় বিরলই বলা চলে। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী এবং একজন শিক্ষিত ও উদারচেতা মহিলা হিসেবে আপনিও আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। পরিস্থিতি বিপাকে কিছু বিরুদ্ধ আচরণ করলেও আজ আমার মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে, আপনাদের পুত্র রণেন এখন আমারও ছেলে। সেইমতো আমার মেয়ে রমিতাও আপনারই মেয়ে। আশা করি, নিজগুণেই আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।
সর্বাঙ্গীন কুশল কামনায় প্রণামান্তে
প্রীত্যর্থী ভূতেশ
এর কিছুদিন পরেই রাঁচি থেকে রণেনের বন্ধুরা আসায়, স্টুডিয়োঘরে বিকেলের চা দিতে এসে মিতা দেখে যে, রণেনসমেত সেই চার-পাঁচজন বন্ধু গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, অদ্ভুত এক দেহাতি সুরে, হাতে তালি দিয়ে এবং নেচে-নেচে সবাই মিলে গাইছে, ‘রনুর–সসুর-কসুর মাপ ক্যরছ্যে… হো- হো মাপ ক্যরছ্যে।’ তার শাশুড়ির কাছে ক্ষমা চেয়ে, সুর নরম করে ওইরকম এক চিঠি ভূতেশ লেখায়, নিশ্চয়ই তার বাবাকে নিয়েই এক বিস্তর ছ্যাবলামি হচ্ছে! এই ভেবে, চায়ের ট্রে-টা কোনওরকমে ঘরের একপাশে নামিয়ে রেখেই, গম্ভীর মুখে নীচে নেমে গেল মিতা। দল বেঁধে সেই প্রমত্ত নাচ না থামালেও রণেন বুঝল যে, সে-রাতে বিস্তর মান ভাঙাতে হবে তাকে। যদিও এটাই তো রণেন বুঝে পায় না, নিজের বাবাকে নিয়ে কেন যে মিতা এখনও এত স্পর্শকাতর!
নতুন গড়ে ওঠা পাড়ারই এক হাসপাতালে প্রসব হল রমিতার। বাপের বাড়িতে সাধ ভক্ষণ এবং দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর পরে, সেই মেয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দুই বাড়ির উপস্থিতিতে যথেষ্ট আনন্দোৎসবও হল; আর তাতেই যেন খুব শান্তি পেল রমিতা। রমিতারা ফিরে এসেছে শুনে, তাদের বাড়ির থেকে সামান্যই দূরে থাকা আর একটি ইশকুল থেকে ডাকও এল, রমিতার; একেবারে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর চাকরি। ইশকুলটা পুরনো হলেও, সম্প্রতি সেটি প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ায়, প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে, এমন একজন দিদিমণি তাদের চাই, যিনি এমএ-বিএড নয়তো এমএ-এমএড পাশ। ওই ইশকুলের পাশেই থাকা রামকৃষ্ণ মিশনের পুণ্যানন্দ মহারাজ নাকি স্বয়ং সুপারিশ করেছেন মিতার নাম। তাঁর বিশেষ পরিচিত রণেনেরই এক শিল্পীবন্ধুর কাছ থেকেই তিনি নাকি জানতে পেরেছেন মিতা সম্পর্কে। পুণ্যানন্দ মহারাজজির সঙ্গে দেখা করে রণেন এবং মিতা— দুজনেরই খুব ভাল লাগল; ভাল লাগল ইশকুলের পাড়া এবং বাড়িটিও। কাজে যোগ দিল মিতা। শুরু হল, নিজের লেডিস-সাইকেলটি চালিয়ে, নতুন ইশকুলে মিতার যাতায়াত। পাড়ার ছোটরা তো মুগ্ধ হয়ে গেল মিতার এই স্মার্টনেস দেখে; এরাই বলতে লাগল, ‘বউদি তো নয়! ঠিক যেন এক রাজপুত্র!’ দিল্লি থেকে আসা মেয়ে বলে, বড়রাও সাগ্রহে মেনে নিলেন, চাকরি করতে সাইকেল ‘ঠেঙিয়ে’ বউমানুষের সেই ইশকুল যাতায়াত। তবে কয়েক মাস পরে, তরুলতা এবং ভূতেশ একযোগে মিতাকে বোঝালেন, মাসকাবারি রিক্সার বন্দোবস্ত করে ইশকুলে যাওয়া-আসা করতে। এ-ব্যাপারে রণেন আর নাক না-গলানোয়, মিতাও তা মেনে নিল অনায়াসে। দুই নাতনিকে নিয়ে সংসার সামলাতে লাগলেন তরুলতা। আর ছুটিছাটার দিনে চুটিয়ে চলল, মিতা আর রনুর সাইকেল বিলাস এবং সাঁতার কেটে গঙ্গায় স্নান।
ইতিমধ্যেই রণেনের মনে হল যে, তাদের বড় মেয়ে ঝিনির জন্য এমন একটা ইশকুল দরকার, যেটা হবে একেবারেই এক অন্যরকম ধাঁচের। এখন তারা মেতে উঠল, একতলার দু’ঘর ভাড়াটে তুলে দিয়ে, তড়িঘড়ি একটা নার্সারি ইশকুল করবার আয়োজনে। সরকারি দপ্তরে খোঁজ খবর নিয়ে তারা জানতে পারল যে, ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছু বেসরকারি উদ্যোগে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থাও। সেগুলির মধ্যে থেকে তারা বেছে নিল, মহিলাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, সেলাই-বোনা এবং জামা তৈরিতে লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স এবং সেইসঙ্গে নার্সারি ইশকুল করবার প্রকল্প। ইশকুলের নাম-সহ রণেনের আঁকা সাইনবোর্ডও ঝুলে গেল তাদের বাড়ির দেওয়ালে। চেনাশোনা বাড়ি থেকে কিছু বাচ্চা এবং উৎসাহী কয়েকজন মহিলাও চলে এল ভর্তি হতে। সেই সঙ্গে যোগ দিলেন দুজন টিচার এবং একজন অ্যাটেন্ডেন্টও। রমিতা মেতে গেল কমিটি, রেজোল্যুশন, কোরাম, অ্যাপ্লিকেশন, গ্রান্ট ইন-এইড— এসবের নিরিখে সব মিলিয়ে একটা প্রশাসনিক চেহারা দেবার কাজে; অন্যদিকে রণেনের মনে হল যে, তার দায়িত্ব হল জনসংযোগের মাধ্যমে চেনাজানা সব বিশিষ্টজনদের এই কাজে সামিল করা। নিজেদের বাড়িতেই এই কর্মযজ্ঞ শুরু হলেও, ভূতেশের উপদেশে রমিতা লেগে পড়ল ইশকুলের জন্য নিজস্ব জমি-জোগাড়ের তদবিরে। জমি পেতে বাদ গেল না মামলা-মোকদ্দমাও। তবে শেষ অবধি সেই মামলা জিতে, ভিতপুজোও হয়ে গেল নতুন ওই ইশকুলবাড়ির। রণেনের নকশায় ক্রমেই সেজে উঠতে লাগল স্লিপ-দোলনাসমেত একটা বড় হলঘর এবং কয়েকটা ক্লাসরুম নিয়ে সেই নার্সারি ইশকুল। একেবারে সাড়া জাগানো হইহই পড়ে গেল, রমিতা আর রণেনের সেই অভূতপূর্ব উদ্যোগে। রণেনের কাকা হরশঙ্করের যোগাযোগে, প্রকাশক দেবকুমার বসুর গ্রন্থজগৎ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল ‘ফটকে’ নামে ছোটদের জন্য লেখা একটি বই; ১৯৪৭ সালে প্রথম অফসেট প্রিন্ট; রণেনের এক বন্ধু, অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্তর লেখার সঙ্গেই ছবি এঁকেছিল রণেন। ইশকুল করবার মাতামাতিতে সে-বইয়ের কথা মনে আসতেই হরুকাকা এবং বিনয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করল রণেন; এত বছর পার করে সে-বইয়ের খুব বেশি কপি খুঁজে না পাওয়া গেলেও, বিনয়বাবু সেদিনই রণেনকে কাজ দিলেন, নতুন কিছু ইলাস্ট্রেশন করে দেবার জন্য । দারুণ উৎসাহে সেসব কাজ শেষ করে, রণেন সেগুলি সময়মতো পৌঁছে দিতেই, বিনয়বাবু বললেন, ছোটদের জন্য বাংলা এবং ইংরেজি বর্ণপরিচয়ের সচিত্র লে-আউট এঁকে আনতে। কিন্তু সে-কাজ আর তার দ্বারা করা হয়ে ওঠা হল না। কারণ, রণেন তখন মেতে উঠেছে ইশকুলবাড়ির আসন্ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে, নাটক-প্যান্ডেল সাজানো-মিতার জন্য বাটিকের শাড়ি তৈরি এবং যোগ্য অতিথি অভ্যাগতদের তালিকা বানাতে। একেবারে নিখুঁতভাবে সেসব সম্পন্নও হল। নানা স্তরের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে রণেনের যোগাযোগ এবং সদালাপের বহর দেখে, একেবারে হতবাকই হয়ে গেলেন ভূতেশ-সহ আরও অনেকেই। সবচাইতে অবাক হলেন তাঁরা, নতুন ইশকুলের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় রণেনকে উদ্দেশ্য করে লেখা, প্রথিতযশা বিজ্ঞানী শ্রী সত্যেন বোস মহাশয়ের আশীর্বাণীটি শুনে; মিতাই সেটি পড়ে শোনাল, সেই প্রকাশ্য সভায়। নতুন ইশকুলবাড়িতে রমরমিয়ে চলতে লাগল তাদের নতুন ইশকুল। স্বজন, আত্মজন, বন্ধুবান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীদের পাশাপাশি, তাদের জীবনে এবার এল, আরও একদল নতুন সঙ্গী; যাদের নাম, ‘কমিটি মেম্বার’।
২
আবার বাঁক এল মিতার জীবনে। ইশকুলের নানা প্রশাসনিক কাজে, প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে মাঝে মাঝেই তাকে যাতায়াত করতে হয় সরকারের শিক্ষাদপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। এখানেই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন দেখা হয়ে গেল, তার বিএড কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে। রমিতাকে খুবই স্নেহ করতেন তিনি। সিমলার চাকরি না নেওয়ায়, মৃদু বকুনিও দিয়েছিলেন সে-সময়ে। এরপরেই নানা সংকোচ এবং কিছুটা বোধহয় অপরাধবোধ থেকেই চিঠিপত্রের যোগাযোগটুকুও বন্ধ করে দেয় মিতা। এদিন দেখা হওয়ামাত্র মিতাকে তিনি তো প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেলেন, আর এক বড়কর্ত্রীর কাছে। তাঁর কাছ থেকে একটি আবেদনপত্র নিয়ে, মিতাকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে কোথায় তা জমা দিতে হবে; বারংবার বলে, তার মনে এও একরকম গেঁথেই দিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই ইন্টারভিউ হয়ে প্যানেল তৈরি হয়ে যাবে; ওইসব নতুন পদে, সেই ভিত্তিতেই নিয়োগও হবে খুব তাড়াতাড়ি। মিতা বুঝতে পারল যে, সরকারি প্রকল্পে অনেকগুলি ‘মাল্টিপারপাস’ ইশকুল তৈরি হতে চলেছে; ইশকুলগুলি গভর্মেন্ট স্পনসর্ড হলেও, প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রীদের পদগুলি কিন্তু পুরোপুরি সরকারি। মিতার বয়স পঁয়ত্রিশ পার হয়নি শুনে, দুজনেই বেশ আশাব্যঞ্জক আলোচনাও করলেন তাকে নিয়ে। ৭৮ নং বাসে করে বাড়ি ফেরবার সেই লম্বাপথ পাড়ি দিতে-দিতেই, মিতা তো মনে-মনে দ্রুত সাজিয়েও ফেলল তার সমস্ত টেস্টিমনিয়াল; এই ভেবে আশ্বস্তও হল যে, বোলপুরের আধা-সরকারি ইশকুলের লিভ ভ্যাকেন্সি এবং ওই বোলপুরেই তার ননদের ইশকুল এবং পরে অনগুলের চম্পতিমুন্ডা— এই দু-দুটো আবাসিক ইশকুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতাও গণ্য করা হবে তার যোগ্যতা হিসেবে; যা থেকে এটাই বোঝা যাবে যে, বার বার চাকরি বদলালেও, কোথাও-না-কোথাও সে কিন্তু কাজ করে গেছে, একটানা! সব শুনে রণেন অবশ্য বলল, ‘আমার মতে তোমার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হল, এই নতুন ইশকুলটি নিজের হাতে গড়ে তোলায়; তিন-তিনটে প্রকল্পের এত্তালা এমন একসঙ্গে যে-মেয়ে পায়, সে কি আর সাধারণ কেউ!’ সংকোচে মাথা নীচু করে আছে দেখে, মিতার দিকে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রণেন বলতে থাকে, ‘বড়-বড় ডিগ্রি বাগিয়ে চাকরি পাওয়াটা এমন কিছু শক্ত নয়! কিন্তু মিতা, ভবিষ্যতের তুমি হয়ে উঠবে একইসঙ্গে একজন শিক্ষাবিদ এবং এন্টারপ্রেনার; কত লোককে যে তুমিই চাকরি দেবে, তা তোমার ধারণাই নেই!’ পাশে রাখা হিটারেই দু’কাপ চায়ের জল টি-প্যানে চড়িয়ে দিতে-দিতে রণেন আবার বলল, ‘তোমার মনে নেই! সেই যে তোমার মা বলছিলেন, কোন কিশোরীবেলায় বাড়ির বাগানের কাঁঠালতলায় ক্লাস বসিয়ে তুমি নাকি ইশকুল-ইশকুল খেলতে! দিল্লি থেকে লম্বা ছুটিতে তোমার বাড়ি আসা মানেই নাকি ইশকুল খুলে জমজমাট ক্লাস বসানো!’
বিকেলের নরম আলোয় নিভে আসছে জানলাজুড়ে লুটিয়ে থাকা, নৌকোভাসানো গঙ্গাটা। রণেনের সামনে ছড়িয়ে আছে, ইলাস্ট্রেশনের পাতাগুলো; বিনয়বাবুর দেওয়া সেই কাজ। ইজেলে টাঙানো একটা নতুন ছবি। বেশ কিছুদিন আগে, রাস্তার পাশের ঝোপে ফুটে থাকা, কচু ফুলের হলুদ কলিগুলো দেখে ভাল লাগায়, তার কয়েকটা তুলে এনে সাজিয়েছিল মিতা; স্টুডিয়োঘরে রাখা, কাঁচকড়ার বড় সেই হলুদ ঘড়াটায়; গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ফুলগুলো সব চুনে-হলুদ রঙের। শুকিয়ে যাওয়ায় সেগুলো তো ফেলেও দিয়েছে কবেই। অথচ সেই ফুলগুলোই আবার সতেজ হয়ে ফিরে এসেছে, রনুর তুলিতে! সত্যিই জাদু জানে রণেন। কালচে-সবুজ ওই রংটাকে কী যে পাগলের মতো ভালবাসে রনু!
৩
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ বলে কথা! যাবতীয় টেস্টিমনিয়ালগুলো নিয়ে মিতা তাই তার বাবার কাছেই গেল, জমা দেবার আগে একবার অন্তত দেখিয়ে নিতে। অবসর এবং মোটা পেনশন— এ-দুটো নিয়ে ফিরলেও ভূতেশ এখন বিশেষ ব্যস্ত, বাড়ির হাতায় একটা সান্ধ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক খোলবার জন্য; সেই সঙ্গে একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন, বাড়ির থেকে মাইলখানেক দূরে পড়ে থাকা কিছু বাস্তুজমি উদ্ধার করে, সেখানেই একটা সবজিখামার বানাতে। তাছাড়াও সম্প্রতি সোদপুর মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই সন্ধেটা তাঁর কেটে যায় অনুমোদনের আগে গাদা-গাদা ফাইল চেক করতে এবং নানাবিধ লোকজনের সঙ্গে দেখা করায়। তবু মিতা আসায় খুবই খুশি হয়েছেন তিনি; তাছাড়াও রণেনের ওপর এখন তিনি খুবই প্রসন্ন, তাঁর নির্বাচনী প্রচারের সময়ে বেশ কিছু পোস্টার সে এঁকে দেওয়ায়। রণেন যদিও ছোট-বড় প্রায় সব দলের পরিচিত প্রার্থীদেরই কিছু-না-কিছু পোস্টার এঁকে দিয়েছে। মিতার অবশ্য এটাই শান্তি যে, ভূতেশের বেলায় সে অন্তত ঘাড় গোঁজ করে বেঁকে বসেনি।
টেস্টিমনিয়ালগুলি দেখার আগে, মিতার ফিল-আপ করা দরখাস্তখানি হাতে নিয়ে ভাল করে চোখ বোলালেন ভূতেশ। মিতার উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘ভাল করে সব দিক ভেবে অ্যাপ্লাই করছ তো!’
‘ভাববার কী আছে? এক ইশকুল থেকে অন্য ইশকুল; দুটোই তো একই পদ! তফাত শুধু সরকারি আর বেসরকারি!’
‘তফাত ঠিক এই জায়গাটাতেই; কারণ সরকারি মানেই বদলি এবং সেটা এ-রাজ্যের মধ্যে যে-কোনও জায়গাতেই হতে পারে।’
‘শুনেছি। ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া বা কৃষ্ণনগরেও হতে পারে; তবে র্যাঙ্ক ভাল হলে প্রথমেই কলকাতায়।’

‘কলকাতাও কি খুব কাছে; মানে নিত্য যাতায়াতের পক্ষে!’
‘মাঝে মাঝেই তো যেতে হয়; এমন কী দূরই বা!’
‘বাড়ি ফিরেও তো কিছু কাজ থাকে! মেয়েদুটোর দেখভাল! দু’দিকেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে!’
‘মামণির তো আপত্তি নেই; আপনি কেন আপত্তি করছেন? তাছাড়া টাকাটাও তো বেশি।’
‘বড়জোর পাঁচশো টাকা বেশি। তার জন্য এই এত বড় হ্যাপা!’
‘আমি ঠিক সামলে নেব।’
‘কী সামলে নেবে! সামলানো যায় না। সংসারটা সবে একটু গুছিয়ে এসেছে; নতুন ইশকুলটাকে ঘিরে কত উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে রণেন! শুনতে পাই যে, পোর্ট্রেট আঁকার ভাল অর্ডার পাচ্ছে। তুমি নড়ে গেলেই কিন্তু সব আবার ভেস্তে যাবে।’
‘শিমলা যাইনি বলে, তখন আপনি কত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন! আর আজ মনস্থির করে, সরকারি চাকরির এই ঝুঁকিটা নিচ্ছি বলে, এখনও আপনি অসন্তুষ্ট!’
‘তখনও তুমি মস্ত ভুল করেছিল, ওই চাকরিটা না নিয়ে; এবং আবার এখনও একটা মস্ত ভুল করতে চলেছ একটা নতুন চাকরির পেছনে ছুটে। ভুলে যেয়ো না যে, তোমার শাশুড়ির বয়স হচ্ছে। আর রণেন কিন্তু সত্যিই তোমাকে অসম্ভব ভালবাসে। তোমার এই সিদ্ধান্তের ফলই যে হবে এক নিদারুণ বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্ভোগ তা তো আমি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।’
‘সামান্য একটা চাকরি বদল, তাতে কেন যে এসব ভাবছেন, সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না!’
‘দেখো, you are my best child… এবং এতে যে কোনওই সন্দেহ নেই সেটাও তুমি ভালই জানো! কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যে, তুমি এখনও চল্লিশও দেখোনি! আমি কিন্তু ইতিমধ্যেই সত্তর দেখেছি।’
আমি মিতা। ভূতেশের মেয়ে, অথবা রণেনের স্ত্রী, বা তরঙ্গনাথের পুত্রবধূ বলে যেসব পরিচয় একের পর এক বহন করেছি এতদিন ধরে, ক্রমে সেসব ছাপিয়ে আমার একটা নিজস্ব পরিচয়ও ঘটছে। ইশকুলের নামের সঙ্গে আমার পদমর্যাদা মিলে গিয়ে, এখন এক ডাকে সকলে চিনছে, আমার নিজেরই নামে। নিজের এই ‘রমিতা’ নামটাই এখন আমার অর্জিত অলংকার। আরও অনেক বড়দিদিমণিদের মধ্যে একমাত্র আমিই সেই রমিতা, ইন্টারভিউতে ফার্স্ট র্যাঙ্ক করে যে এই সরকারি চাকরিতে এসেছে। ফলে কলকাতা এবং সোদপুরের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যেও আমি এখন পরিচিতি পাচ্ছি এভাবেই, যেখানে আমার নামটাই যথেষ্ট; ফলে, নামের সঙ্গে ঝুলে থাকা যাবতীয় যা লেজুড় ঝুর–ঝুর করে কেমন খসেও পড়েছে সেসব! প্রবল উৎসাহে হাল ধরেছি নতুন এই ইশকুলটাকে গড়ে তোলার কাজে। নানা নদীর জলের মতো আমার ভাবনায় এসে মিশেছে, গৃহশিক্ষক জীবন মাস্টারমশাই ছাড়াও, মিস দোয়ারা, শান্তি দত্ত, বিভুরঞ্জন গুহ, অনাথনাথ বোস, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, মালতী চৌধুরী, মেরি উইলফ্রেড— এমন সব মহার্ঘ শিক্ষাবিদদের ভাবনার স্রোত। তাছাড়াও বাংলা–ইংরেজি–হিন্দি বাদেও কিছুটা ওড়িয়াও তো জানি। রণেনের উৎসাহে, তারই এক বন্ধুর যোগাযোগেই সংস্কৃততে আদ্য–মধ্যও পাশ করে গেছি ইতিমধ্যেই। ফলে, এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া; এবং সমস্ত পিছুটান ফেলেই।
রণেন আমাকে খুবই সাহায্য করে; অনেক আলোচনাও করতে চায়; কিন্তু এটাই সে বুঝতে পারে না কিছুতেই যে, আমার এই কাজে রণেনকেও আর একেবারেই প্রয়োজন নেই। এমনকী ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে, এক পট চা নিয়ে তার সঙ্গে ছাদে বসে–বসে গল্প করবার থেকেও, আমার তো বেশি ইচ্ছে করে, টুক করে একটু ঘুমিয়ে নিতে। রণেনের গল্প, রাগ বা অভিমান সবেতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি আমি।
আমি তো এটাও ভেবে পাই না যে, ওইরকম একটা পুলিশিপদে থেকেও, সন্ধেবেলা কী করেই বা আবার গান গাইতে বসতেন রায়সাহেব শ্বশুরমশাই! আমার গত জন্মদিনে, তার বাবার গানের খাতার থেকেও সুন্দর, চামড়ার কারুকাজ করা যে-খাতাটা রণেন আমাকে বানিয়ে দিয়েছিল, সেটারও তো সব ক’টা পৃষ্ঠাই একেবারে ফটফটে সাদা। তিন–চারদিনের প্রবল পরিশ্রমে ঠুকে–ঠুকে বানানো কাঠখোদাই করা বাক্সসমেত ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মটাও পড়ে আছে ঘরের কোণে। আমি গান গাইব বলে, ওটাও রণেনেরই কিনে দেওয়া উৎসাহ করে।
ইতিমধ্যে দুই মেয়ের নার্সারি–পাঠ শেষ হলে, কলকাতার ইশকুলে ভর্তি করে দিই ওদের; থাকবার ব্যবস্থা হয় ছোটননদের বাড়িতে। ইস্কুলবাসের বন্দোবস্তও হয়ে যায়; নিজের ইশকুল ছুটি হলে ওদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করে, তবে সোদপুরে ফেরা; শরীর–স্বাস্থ্য ভাল থাকলেও লেখাপড়া প্রায় দুজনেই ছেড়ে দিতে শুরু করে। মেয়েদের কাছে না–পেয়ে রণেনও বসে থাকে মনখারাপ করে। শেষে নিজে–নিজে ঠিক করেই বড় মেয়েকে হস্টেলে দিয়ে, ছোটকে ভর্তি করে নিই আমারই ইশকুলে। সোদপুর থেকে কলকাতা যাতায়াত শুরু করে, ছোটটা একেবারে ঝিমিয়ে পড়ছে দেখে, কলকাতায় বাসা ভাড়া করে, ওকে নিয়েই থাকতে শুরু করি; আমার দরকারে লাগবে বলে বাড়ির ফার্নিচারও নিয়ে যেতে বলেন আমার শাশুড়ি। রণেন তবুও বোঝে না যে, তার থেকে কতখানি দূরে সরে যেতে চাইছি আমি! ভেবেছিলাম এরকম একটা ধাক্কা খেলে সে–ও হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে। তবু সেই নিয়ম করে আমার জন্য শাড়ি–ব্যাগ সব বানিয়ে যাচ্ছে। রণেন এটাও বোঝে না যে, দোকানে সাজানো কিছু–কিছু জিনিস দেখে তা যে আমারও কিনতে ইচ্ছে করে। সব কিছুতেই বিশিষ্ট হয়ে কি বাঁচা যায়!
আর এক উৎপাত হয়েছে, মনকেমন করলে থেকে–থেকেই তার সঙ্গে দেখা করতে বড়মেয়ের হস্টেলে গিয়ে রণেনের ওই যখন-তখন হাজির হওয়া; হস্টেলের দারোয়ান থেকে সুপার অবধি সকলকে এমনই জাদু করেছে যে, রণেন গিয়ে দাঁড়ালেই ঝিনিকেও তাঁরা পাঠিয়ে দেন ভিজিটার্সরুমে। সেখানে যাতে নিয়মিত যেতে পারে, সেজন্য ওই অঞ্চলেরই একজনকে আঁকা শেখানোর টিউশনও জোগাড় করে নিয়েছে রণেন। ঠিক ওই একইভাবে ছোটমেয়েকে দেখতেও যখন–তখন সে চলে আসে আমার কলকাতার বাসায়। বেশি দেরি হয়ে গেলে, ঠেকায় পড়ে কোনওরকমে রাতটুকু কাটালেও পরদিন ভোরে উঠেই, তড়িঘড়ি সে ফিরেও যায় নিজের আস্তানায়। তাকে নিয়ে, অদ্ভুত এক অস্থিরতা এবং সেই সঙ্গে বিরক্তি— ঘিরে ধরছে আমাকেও। কলকাতায় থেকেও যেন আমি পরাধীন; সংসারের বাঁধনটাই যেন ফাঁস হয়ে চেপে বসছে আমার চতুর্দিকে।
এরই মধ্যে তোড়জোড় করে, কলকাতায় একটা প্রদর্শনীও করে ফেলল রণেন। যেটুকু যা বিক্রি হল, সে-টাকায় এক জোড়া বালা গড়িয়ে দিল আমাকে; বাড়ির স্যাকরাকে ডেকে নিজেরই নকশায়। সপ্তাহান্তে দুই মেয়েকে নিয়ে সোদপুরে আমার যাওয়া অনিয়মিত হয়ে গেলেও, এখনও প্রতিদিন বিকেলে আগের মতোই, চায়ের পট সাজিয়ে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছাদে বসে থাকে রণেন; এততেও সে, এখনও আমার ঘরে ফেরার অপেক্ষায়!
বছর বারোর বড়মেয়ে হোস্টেল থেকে চলে এসে, রণেনের কাছেই থাকে; ওখান থেকেই ইশকুল যায় দুটো বাস বদল করে; একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে রণেনের হাঁটাচলাও অনেক কমে গেছে; মেয়ে কাছে থাকায় এবং ভাড়াটেদের ভরসায় সে তবু চালিয়ে নিচ্ছে, নিজের মতো করে। আমাদের দোতলার সংসারের পাট উঠে গিয়ে, ইদানীং সেখানেও এক ভাড়া বসেছে। প্রিভেসি নিয়ে স্পর্শকাতর রণেনও আর আপত্তি করে না, তার সেই স্টুডিয়োঘরটাতে অন্য কেউ ঢুকে এলে। অবারিতদ্বার সেই ঘরটাতেই সর্বক্ষণই সে শুয়ে–বসে থাকে, কারোর-না-কারোর অপেক্ষায়।
সকলে মিলে একসঙ্গে কাটানো এটাই সেই শেষ পুজোর ছুটি; ঝিনিকেও বুঝিয়েছি হস্টেলে ফিরে যাবার জন্য; বুঝিয়েছি রণেনকেও, কলকাতায় গিয়ে যাতে আমার বাসাতেই থাকে। তবে নতুন পরিকল্পনা আর কাজে লাগল না; কারণ, পুজোর ছুটি শেষ হবার আগেই, দ্বিতীয় স্ট্রোকেই চলে গেল রণেন। সোদপুরের পাট তুলে দিয়ে, মামণি আর দুই মেয়েকে নিয়ে, পাকাপাকিভাবে চলে এলাম কলকাতায়।
রণেন কি কিছু বুঝেছিল! প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা ক্যানভাসে তার আঁকা শেষ ছবিটা দেখিয়ে হাসতে–হাসতেই কেমন বলেছিল, ‘এই ছবিটার নাম?’ ‘গলায় দড়ে’। অবাক হয়ে দেখেছিলাম, বামন–মাপের লোকটা গলায় একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে, তার মাথার ওপরে অনায়াসে কেমন নিজেই সেটাকে টানছে! লোকটার পাগুলো মিজেটদের মতো হলেও সে কিন্তু নাচছে! আর তার হাতদুটো অসম্ভব সবল এবং দেহ আন্দাজে প্রকাণ্ড লম্বা; একইসঙ্গে এক অদ্ভুত প্রশান্তি তার চোখেমুখেও। আরও অবাক লেগেছিল, ওই ছবিটার রং দেখে। লোকটার পায়ের নীচে একফালি গাঢ় সবুজ ঘাসের আভাস দু’পায়ে ঠেলে দিয়ে, খর্বদেহ সেই বামুন কিন্তু উদ্বাহু। আর বাকি ক্যানভাসজুড়ে শুধুই উজ্জ্বল হলুদ! এমন আলো তো কক্ষনো আঁকেনি রণেন! আর এও বড় আশ্চর্য যে, রণেন চলে যাবার পরে– পরেই, দড়ি ছিঁড়ে হুড়মুড় করে, ছবিটা যেন দেওয়াল থেকে একেবারে মুখ থুবড়ে এসে পড়ল মেঝেতে। কিছু একটাতে খোঁচা লেগে, খসে পড়বার সময়তেই মস্ত একটা গর্তও হয়ে গেল ছবিটায়। ভীষণ জোরে আর্তনাদ করে, ডুকরে–ডুকরে কাঁদতে লাগল ঝিনি।
কলকাতার ছোট্ট বাসায় শুরু করলাম যে জীবন, সে তো এক অন্য রমিতা! তবু, বাবার বলা সেই কথাটাই কেন যে বার বার মনে পড়ে— ‘তুমি এখনও চল্লিশও দেখোনি!’ সত্যিই কি তাই! আমি চল্লিশে পৌঁছবার আগেই, বিষণ্ণ সেই হুকার’স গ্রিন রংটাকে লাথি মেরে নিজেই তাড়িয়ে, রণেন কি আমাকে দিয়ে গেল, এক মুঠো উজ্জ্বল হলুদ; তার অন্তিম–উপহার হিসেবে!
আমার এই মধ্য উনচল্লিশেই একইসঙ্গে তা কি নয়, এক আশ্চর্য মুক্তিও!
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র