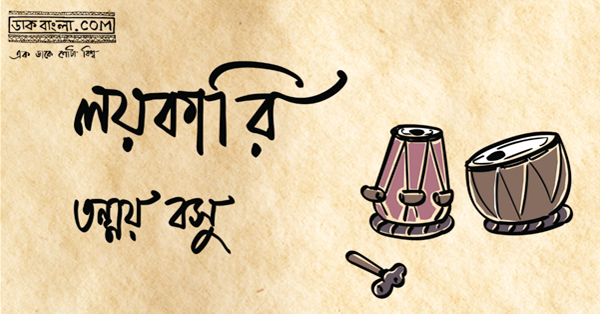রাতবিরেতে সেই মোহিতে
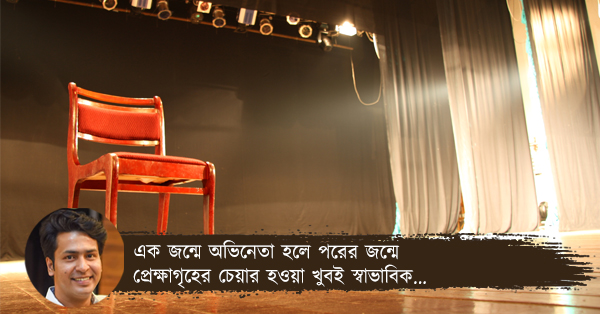
 অনির্বাণ ভট্টাচার্য (March 27, 2025)
অনির্বাণ ভট্টাচার্য (March 27, 2025)প্যাঁচে পড়ার আওয়াজ হল ‘ক্যাঁচ’
এই প্রকার শব্দ করেই আমার বাড়িমুখো উবের থামল টালা ব্রিজের ওপর। পাশে বসা আমার সহ-অভিনেত্রী বা তার চেয়ে কিঞ্চিত বেশি। সে প্রশ্ন করে বসল— কী হয়েছে?
আমি বললাম— আমাকে নেমে যেতে হবে।
সে— কেন? পায়খানা পেয়েছে?
আমি— আরে না না!
সে—তবে? কাউকে সময় দিয়ে রেখেছ? সে আসবে, না কি তুমি তার কাছে যাবে?
আমি— আরে ধুর! খুবই দরকার, নামতে হবে। তুমি চলে যাও।
এই বলে তার হাতে একটি একশো ও একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে তার কৌতূহলের আর্ত তৃষ্ণা একবিন্দু না মিটিয়েই নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। উবের এগিয়ে গেল দক্ষিণ কলকাতার দিকে।
এই লেখকের আরও লেখা : এই নতুন দেশ কি ইরফান খানকে ধারণ করতে পারত?
গোপন কারণ
আমরা ফিরছিলাম পাইকপাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চ থেকে। ‘অদ্য শেষ রজনী’-র অভিনয়ে শেষে। ‘শো’-এর পর প্রশংসার রাজভোগ সহকারে চা খেতে খেতে সেদিন একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছিল। গাড়িটি আমাদের নিয়ে টালা ব্রিজে উঠতেই আমার খেয়াল পড়ল, মোহিত মৈত্র মঞ্চের সাজঘরে আমি আমার হৃৎপিণ্ডর খানিকটা অংশ ও নাভিস্থলে জমানো স্বল্প বাতাস ভুল করে ফেলে এসেছি। ‘শো’-এর শেষে তাড়াহুড়ো করে বেরতে গিয়েই এই গেরো। এমনিতে পরের রবিবার এসে অভিনয়ের আগে সেগুলো যথাস্থানে ফিট্ করে নিলেই হত। কিন্তু খেয়াল হল, আগামী পরশু ‘অথৈ’ নাটকের অভিনয় অ্যাকাডেমি মঞ্চে। ফলে, সেগুলি আমার লাগবেই। অগত্যা, টালা ব্রিজ থেকে আমি হাঁটা লাগালাম মোহিত মৈত্র মঞ্চের উদ্দেশে।
‘যেখানে যে-কোনও ভয়
সেখানেই সন্ধে হয়’
মোহিত মৈত্র মঞ্চের রেলিং টপকানো গেল, কিন্তু মূল ফটক বন্ধ। আশপাশে কাউকে দেখতেও পাচ্ছি না। ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পেলাম না। এপাশ-ওপাশ খানিক হেঁটে বেড়ালাম। হঠাৎ দেখলাম, হলের ডানদিকের দেওয়ালে, যেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড মোটরবাইকের পার্কিং লটের দরজাটা, ঠিক সেখানে একটি সাদা বেড়াল দাঁড়িয়ে আছে, এবং তার গায়ে বাঁ-দিক থেকে ‘গডফাদার’ ছবির মতো হাফ লাইটিং।
তার মানে দরজাটা খোলা?
এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, অনুমান ঠিক। খোলা দরজা দিয়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের ডানদিকে অবস্থিত বড় দু-পাল্লার দরজায় ঠেলা দিতেই আমি পৌঁছে গেলাম লক্ষ্যস্থলে।
‘কার লাগি হে সমাধি তুমি একা বসে আছো আজ’
আমায় যেতে হবে, মঞ্চের বাঁ-দিকের সাজঘরে। আমি আছি ডানদিকে। মঞ্চ পেরতে হবে। ঝাঁপ দিলাম। মায়ানদীর মাঝখান অবধি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাকালাম দর্শকাসনের দিকে। এস্থানে কবি হলে, পকেট থেকে কাগজের টুকরো আর কলম বের করে দু-পঙক্তি লিখে ফেলত। ঔপন্যাসিক, কাহিনির প্লটভাগ করে ফেলত এবং আঙুল মটকে ওয়ার্ম-আপ করে নিত। গায়ক গেয়ে উঠত এককলি কানাড়া। নৃত্যশিল্পীও একটা ধেই-পাক দিয়ে মেখে নিতে পারত এই শূন্যতা। কিন্তু আমি তো এখন ‘কেউ না’। খানিক আগেও ছিলাম গোকুলের ষাঁড়, ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। জন হেনরি-র মতো টগবগে রক্ত নিয়ে, তুঘলকি মেজাজে খামচে ধরেছিলাম কয়েকশো টুঁটি। মনে মনে বলেছিলাম, স্কিল্ দ্যাখ, স্কিল্। যা শিখেছি, যা জেনেছি, করায়ত্ত করেছি যত পয়জারি, যত কালোয়াতি— সব একে একে বাণের মতো ধেয়ে যাবে আমার তূণ থেকে তোদের হৃদয় লক্ষ করে। পালাবি কোথায়? তুই কাঁদবি না, তোর বাবা কাঁদবে।
তবে, সে তো ঘণ্টাদুয়েক আগে। পর্দা মাটিতে ছুঁতেই তো আমি এক পরিচয়হীন শরীর হয়ে গেছি। হয়ে গেছি শূন্য। শূন্য যোগ করে করে শূন্যই হয় জানি। ফলত, এই মহান শূন্যতার ভেতর ‘অনাটকীয় শূন্য’ হয়ে, এই বিরাট দানবীয় ‘একা’-র সামনে আমি লিলিপুট একাকিত্ব নিয়ে খানিক গরুর মতো চেয়ে থাকলাম।
বেশ খানিকটা সময় চেয়ে থাকার পর আমার চোখ, আমার চোখে খোঁচা মেরে বলল— ‘চল ভাই, ঘুম পেয়েছে!’
আমিও স্থবিরতা ভেঙে সাজঘরের দিকে চললাম। দু-পা ফেলতেই কানে এল, ‘বড্ড ওপর ওপর হচ্ছে হে পার্টটা।’
ঘুরে তাকালাম।
চোখ বলল— ঘুম ছুটে গেছে।
মন বলল— ভয় পেয়ে গেছি ভাই।

চেয়ার-ম্যান
মঞ্চের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডানদিকের প্রথম সারির প্রথম চেয়ারটি থেকে কথাটা ভেসে এল—
আমি রাম বা মোদি, কারও একটা নাম জপতে যাব, তখনই আবার কণ্ঠ—
চেয়ার: কম বাজেটের হরর ফিল্মের মতো করে রেখেছ কেন মুখটাকে? চেঁচিয়ে-টেঁচিয়ে একাকার করো না আবার। একা আছ দেখছি, তাই দুটো কথা বলার সাধ হল, যদিও বেশি সময় নেই। উনি এলেন বলে…
আমি : আপনি কে?
চেয়ার : দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি চেয়ার!
আমি : আপনি কথা বলছেন কী করে?
চেয়ার : তুমি যেভাবে বলছ, কণ্ঠ, মুখ, শ্বাস, প্রশ্বাস, ভাষা ইত্যাদির সাহায্যে…
আমি : ও…
চেয়ার : বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার বলে দেখো, বিশ্বাস হচ্ছে না…
আমি : না না পাগল নাকি! হচ্ছে বিশ্বাস, দারুণ বিশ্বাস হচ্ছে। ওই তো দেখতে পাচ্ছি, আপনার মুখ নড়ছে, বুক উঠছে, নামছে…
চেয়ার : হেঃ হেঃ হেঃ। যাক, তাড়াতাড়িই লাইনে এসেছ। তা তোমার নামই তো অনির্বাণ?
আমি : আজ্ঞে হ্যাঁ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য।
চেয়ার : অ, বামুন…
আমি : হ্যাঁ, মানে, কিন্তু আমি ওসব মানি না।
চেয়ার : তাতে আর কী যায় আসে? সবই ফ্যাশনের অঙ্গ… যাক গে, নাকের তলায় সরু গোঁফ এঁটে যে পার্টটা করছ, এবং টুকটাক নামও কুড়িয়েছ শুনেছি, তা তোমার নিজের কী মনে হচ্ছে?
আমি : আজ্ঞে, নিজের মুখেই বলব?
চেয়ার : অন্য কারও মুখ পকেটে করে এনেছ? না কি তুমি আধুনিক ব্রহ্মা, চুলের তলায় আরও তিনটে মুখ আছে? বাচাল, আঁতেল কোথাকার (রাগত)!
আমি : (নরম করে) আচ্ছা বলছি, আমার মনে হচ্ছে… আমার অভিনয় মানুষের ভাল লাগছে।
চেয়ার : তোমার অভিনয় তো ঘোড়া, ব্যাং বা টিকটিকি দ্যাখে না, ফলত ভাল বা খারাপ যা-ই লাগবে, মানুষেরই লাগবে। এ আর নতুন কী!
আমি : না মানে, মানুষের ভাল লাগছে মানে, নিশ্চয়ই ভালই করছি…
চেয়ার : ও আচ্ছা। বুঝেছি…
আমি : কী বুঝলেন?
চেয়ার : বুঝলাম যে, তুমি কোন মসজিদের মোল্লা, আর তোমার দৌড় কতটুকু!
আমি : না শুধু তাই নয়, আমি কিন্তু সবসময়ই আরও উন্নতি করার চেষ্টা করি, আরও আরও কী করে বেটার করা যায়-
চেয়ার : হুমম্। কর্পোরেট থিয়েটারের যুগে তা না করেই বা উপায় কী, সুতোতে মাঞ্জা কম হলে দাগ কাটবে কী দিয়ে— তবে আমার বাপু মনে হচ্ছে, তুমি বড্ড টেকনিক-নির্ভর, হৃদয় কম তোমার। দুঃখ বেরচ্ছে, কিন্তু তাও যেন একটা যন্ত্রের মাধ্যমে। মানুষ-মানুষ ভাবটা কম…
আমি : আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু মহামান্য চেয়ার, আপনি যদি ব্রেখট-পরবর্তী অভিনয়টা সারা পৃথিবীর নিরিখে একবার…
চেয়ার : (বিদেশি কপচিও না) অভিনয়ের শেষে তাহলে দর্শককে ‘আধুনিক অভিনয়ের ধারা বিবর্তন’ নামক হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করতে হবে। আমি যেটা বলছি, সেটা তুমি মানলে না, উল্টে দিলে তাত্ত্বিক তর্ক জুড়ে, বলা যায় না, কাল কোনও একটা সেমিনারে গিয়ে আমার বাপ-বাপান্তও করতে পারো।
হল না, হল না বুঝলে, তোমাদের যুগ সম্মান শিখল না, সহবৎ শিখল না, শুধু অহং, আত্ম-উদযাপন আর ঔদ্ধত্য। হল না, হল না, কিস্যু হল না।
আমি : আহা হা, আমি শুনব না কেন? সমালোচনা তো শুনতে হবেই, আমি জাস্ট একটা আলোচনা শুরু করতে চাইছিলাম।
চেয়ার : ঘেঁচু শুরু করতে চাইছিলে, কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিজের বিদ্যে জাহির করতে চাইছিলে… আর আমি বলেই এসব পারছ। আমার দাড়ি নেই, কমিউনিস্ট বা অ্যান্টি সিপিএম ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, পিআর নেই, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। তাই আমায় ‘কিছু না’-র দলে ঠেসে দিয়ে লেকচার-চাপা দিতে চাইছ।
এই তো ক’দিন আগে এক প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তোমার বাচনভঙ্গির সমালোচনা করলেন দৈনিকে, তাকে ওই অভিনয়ের হ্যান্ডবিলটা পড়ে শুনিয়েছ?
আমি : (জিভ কেটে) আরে, কী বলছেন। উনি নিজে মস্ত বড় অভিনেতা, বাংলাদেশে অমন অভিনেতা কম আছে, আর সর্বোপরি, উনি চলচ্চিত্র পরিচালক, নামী দৈনিক, আমি কি পাগল?
চেয়ার : (প্রচণ্ড রেগে) না, তুমি সেয়ানা, অভিনয়ের চাড্ডি মারপ্যাঁচের সঙ্গে এগুলোও বেশ শিখে গেছ।
আমি : (প্রচণ্ড নাছোড় হয়ে) এগুলো শিখে নিতে হয় চেয়ারকাকু। অপুও সময়মতো শিখে নিয়েছিল, মায়ের শ্রাদ্ধটা কালীঘাটে করে নেওয়া যায়। এফেক্টিভ বাবা-কাকাহীন এই আলোর দুনিয়ায় বোকা ‘সেজে’ থাকা যায়, বোকা ‘হয়ে’ থাকা যায় না।
লাথিয়ে দেওয়ার জন্য হাজারো পা আছে, এগুলো সব অনিচ্ছা-লাথি, কেউ ভাবল রাস্তা থেকে পা দিয়ে ইট সরিয়ে দিলাম, ইটের জায়গায় মানুষও থাকতে পারে, প্রতিভাও থাকতে পারে।
যতই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হোক না কেন, কোনও না-কোনও একটা রেসের মাঠে আমাকে ঢুকতেই হবে, নীল, লাল, হলুদ, সবুজ যে-কোনও রঙের ঘোড়া কিংবা নিদেনপক্ষে খচ্চর বা গাধার পিঠে চড়ে রেসটায় থাকতে হবে। একালে মিটিমিটি হাসি মুখ নিয়ে বসে থাকেন কেবল বুদ্ধ।
দার্শনিকদের যুগ শেষ কাকু। এটা ক্রেতা যুগ। দোকান সবসময় খোলা। দোকানে ঢোকার, দোকানে থাকার, এবং যথাসময়ে বিক্রি হওয়ার প্যাঁচপয়জার যে শিখে নিতেই হবে। সে আপনি পোশাক হোন বা ম্যানিকুইন। দোকান-দোকান খেলায় আপনাকে পড়তে হবেই।
চেয়ার-জন্ম বলে এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেন, জন্মাতেন মানুষ হয়ে, বুঝতেন। অভিনেতা হলে তো কথাই নেই। হাততালি, সমালোচনা, আর টাকার খাম ছাড়া কিছুই জুটত না। আরও কিছু যে জোটা দরকার, সেসব কেউ বুঝত না, বুঝলেন?
আপনি স্থির, তাই শুনছেন। আমি হাঁটছি, দৌড়চ্ছি, আছাড় খাচ্ছি, কানে লেগে থাকছে বিষাক্ত বাতাসের শব্দ, তাই ইচ্ছে থাকলেও সব শোনা যায় না, বুঝলেন কাকু?
চেয়ার-জন্ম বলে এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেন, জন্মাতেন মানুষ হয়ে, বুঝতেন। অভিনেতা হলে তো কথাই নেই। হাততালি, সমালোচনা, আর টাকার খাম ছাড়া কিছুই জুটত না। আরও কিছু যে জোটা দরকার, সেসব
কেউ বুঝত না, বুঝলেন?চেয়ার : লাথি আমি মারতে পারি না, আমার পা সিমেন্টের ঢালাই-এর ভেতর, আর তোমাদেরই এক কবি-মহোদয় নাটক দেখতে এসে সর্বক্ষণ কনুইয়ের ভর দিয়ে আমার ডান হাতলটাকে জখম করে গেছে, না-হলে এক রদ্দায় এসব ভাষণ-বুলি বন্ধ করে দিতাম।
আমার স্থবিরতা নিয়ে আমি গর্বিত। আমার শ্লাঘার কারণ স্থিরতা। আমি ‘দ্রষ্টা’। বুঝলে হে? অবশ্য যে যুগ শুধু অভিনেতা, ক্রিকেটার আর মন্ত্রীদের নিয়ে মেতে থাকে, তারা দ্রষ্টার অর্থ বা প্রয়োজনীয়তা কী বুঝবে?
কী করে তোমার মতো বাচালরা বুঝবে, শূন্যতার ভেতর অবিরাম তাকিয়ে থেকে শূন্যেরই মাত্রাভেদ ঘটতে দেখার মজাটা কী!
যখনই শূন্যস্থান পূরণ হয়, তখনই আমার চোখ ঢেকে দেয় বিভিন্ন পিঠ ও পশ্চাৎ, যেহেতু আমি প্রথম সারি। কিন্তু সেসব উঠে গেলেই আবার শূন্যের মুখোমুখি আমি।
আমি : (মাতালের মতো) শুনুন কাকু, কলিকাল স্যাচুরেশন পয়েন্ট মিট করে গেছে, ওইসব শূন্য-পদ্যের কোনও মূল্য নেই। খুব ভালভাবে বুঝতে পারছি, স্থির-স্থবির-ব্যর্থ— এই তিনটে নেগেটিভ শব্দকে কবিতার স্টাইলে বলে গ্ল্যামার কাড়তে চাইছেন।
আমি চুপ করে আছি, আমি দেখছি, আমি অনড়, আমি অন্ধকারে, তাই আমি ভাল।
সব বুঝতে পারি কাকু, ভাল অভিনয় না করতে পারি, কিন্তু কে কখন কোন পরিস্থিতিতে কী অবস্থান নিচ্ছে, হালের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আমাদের ভাল করে শিখিয়ে দিয়ে গেছে।
আরে মশাই, পরাজয় আর আলস্যের ওপর ওসব কেরদানির চাদর চাপা দিচ্ছেন কেন? ক্ষমতা থাকলে দৌড়ন, মিশে যান সবার সঙ্গে, থুথু ছেটান অন্যের গায়ে, অন্যের থুতু নিজের গায়ে মাখুন। সময় থাকতে চলে আসুন, জেনে রাখুন, কয়েককালের মধ্যেই মানুষ মানুষেরই মাংস খাওয়া শুরু করবে। এই ক্লান্তিহীন ম্যারাথনে যে ধীরে দৌড়বে, তাকে আমরা ধরব, মারব, থ্যাঁতলাব, কাটব, অল্প সেদ্ধ করে ছিটিয়ে দেব পেঁয়াজ-লঙ্কা। শুরু হবে সর্বজনীন মাংস উৎসব। গ্যাঁট হয়ে, চুপচাপ বসে না থেকে শামিল হোন সেই উৎসবে। ক্ষমতায় কুলোলে, আসুন, দৌড়োন—
চেয়ার : ক্ষমতার কাছাকাছি অর্থের একটা শব্দ আছে জানো? সেটা হল, ‘শক্তি’। কিন্তু সে শব্দের জোর ক্ষমতার থেকে বেশি, তা যদি বুঝতে, তবে এই পার্টটা এমন ওপর-ওপর করতে না।
না গো, তোমাদের মাংস উৎসবে আমি নেই। তোমাদের দৌড়কে আমি ঘৃণা করি। আর তাছাড়া, তোমরা যে হত্যালীলায় মাতবে, তা দ্যাখার জন্য তো কাউকে চাই রে বাবা, যে গল্পটা বলবে পরের শতাব্দীর তোমারই মতো কোনও দৌড়বীরকে। ফলত, তুমি বা তোমরা দৌড়ও। ফোলাও ক্ষমতার পেশি, আমি আমার শান্ত শক্তি নিয়ে ভালই আছি। তোমাদের এই হনহনানি দৌড়ে আমি নেই, এ জেনে আমার সুখ। বা রে, তুমি তো কোন ছার, তোমাদের ওই পরিচালক। উফ্! কী দৌড়ই না দৌড়চ্ছেন! আমার কোলে বেশ কয়েকবার এসে বসেছে বলেই জানি, সর্বক্ষণ কাঁপছেন, থরথর করছে শরীর। আর গরম গা, শতাব্দীর জ্বর যেন ওর গায়ে লেগে গেছে, আচ্ছা, উনি অমন কেন জানো?
আমি : আমি ঠিক জানি না, তবে অনুমান করতে পারি, উনি বুদ্ধ বা বাল্মিকী হতে চাননি, চাননি জীবনানন্দের মতো ধীরে পথ চলতে। ঝড় হতে চেয়েছেন। আমি জানি না, হয়তো তাই চেয়েছেন।
চেয়ার : আচ্ছা উনি খুব রাগী, তাই না? কেন এত রাগ ওঁর…
আমি : জানি না।
চেয়ার : কার ওপর রাগ?
আমি : বোধহয় দোকানের ওপর।
চেয়ার : যে দোকান উনি গড়ে তুলেছেন বা যেখানে উনি বসেন, সেগুলোর ওপরও?
আমি : আমার মনে হয় সেগুলোর ওপরেই বেশি রাগ।
চেয়ার : হ্যাঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। চিনি তো, ফি-সপ্তাহে এমন লোকের সঙ্গেই তো রাতটা কাটে, একরকম।
আচ্ছা এরা এমন কেন হয় বলো তো?
আমি : জানি না।
চেয়ার : আন্দাজও করো না?
আমি : আমার মনে হয়, এরা ‘সাদা’-কে সাদা দ্যাখেন এবং এদের হৃদয় চিরকাল শকুন ও শেয়ালের খাদ্য।
চেয়ার : হুমম, আসলে এরা বেঁচে থাকতে থাকতেই মৃত্যুকে উদযাপন করতে পারেন। মানে ধরো, সবই করছেন, কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই বিনাশের একটা খেলা চলছে যেন।
জীবনের চরম সাফল্যমণ্ডিত মুহূর্তগুলিতে বিনাশ এসে উঁকি মেরে যাচ্ছে। নতুন নতুন সবুজ চারাগাছ আর হাইড্রোজেন বোমা একই সঙ্গে নির্মিত হচ্ছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একসাথে। সাধু ও শয়তান গলা জড়াজাড়ি করে লীলা দেখাচ্ছে।
আমি : আপনার পূর্বজন্ম অভিনেতার নাকি! এত কথা জানলেন কী করে? অবশ্য এক জন্মে অভিনেতা হলে পরের জন্মে প্রেক্ষাগৃহের চেয়ার হওয়া খুবই স্বাভাবিক!
আমার তো প্রথমটায়, চেয়ার সারির দিকে তাকিয়ে মৃত-অভিনেতাদের কবরখানা মনে হয়েছিল। অ্যাই, আপনি কে বলুন তো?
না গো, তোমাদের মাংস উৎসবে আমি নেই। তোমাদের দৌড়কে আমি ঘৃণা করি। আর তাছাড়া, তোমরা যে হত্যালীলায় মাতবে, তা দ্যাখার জন্য তো কাউকে চাই রে বাবা, যে গল্পটা বলবে পরের শতাব্দীর তোমারই মতো কোনও দৌড়বীরকে। ফলত, তুমি বা তোমরা দৌড়ও। ফোলাও ক্ষমতার পেশি, আমি আমার শান্ত শক্তি নিয়ে ভালই আছি।
চেয়ার : হেঃ হেঃ। ভালই এগচ্ছে, কিন্তু তোমায় হতাশ করলাম ভায়া, আমি কেউ নই, চেয়ারই।
আসলে প্রতি শো-এর রাতে উনি আসেন, খবরাখবর নেন, উনিই বলেন এইসব ভারী ভারী কথা। উনিই আমায় প্রথম বলেন ‘আত্মধ্বংসের আলো’-র কথা, আচ্ছা, তুমি তো খুব ডেঁপো, আত্মধ্বংসের আলো কেমন হয় জানো?
আমি : না। জানি না। সুদীপদা জানতে পারে। আর আমি ডেঁপো নই।
চেয়ার : গোলাপি আর নীল মিশিয়ে একধরনের আলো। ব্যাপারটা ধ্বংসের। কিন্তু আলোটা খুব নরম, খুব মিষ্টি।
আমি : ও আচ্ছা, হবে হয়তো।
চেয়ার : তাহলে তুমি আত্মধ্বংসের আলো চেনো না?
আমি : না, সুদীপদা চিনতে পারে।
চেয়ার : তাহলে অমিয় চক্রবর্তীর রোল করো কী করে? সেটা তো সুদীপদা করে না।
আমি : করি ধারণা থেকে, স্কিল থেকে, ঘাম ঝরিয়ে, খাম পাব বলে!
চেয়ার : এঁড়েমো করছ কেন? ঘুম পাচ্ছে?
আমি : আজ্ঞে হ্যাঁ। টানা দু’ঘণ্টা অভিনয় করতে গেলে কষ্ট হয়। হৃৎপিণ্ডে ও নাভিস্থলে চাপ পড়ে, এতটা কষ্ট হত না, আসলে হৃৎপিণ্ডের খানিকটা অংশ আর নাভিস্থলে জমানো স্বল্প বাতাস গ্রিনরুমে ফেলে গেছি, সেটাই নিতে এসেছিলাম। ফালতু ঢপের সেমি-দার্শনিক আলোচনায় দেরি হয়ে গেল।
চেয়ার : আমার ডান-হাতলটায় ব্যথা না থাকলে…
আমি : (থামিয়ে দিয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, ব্যথা না থাকলে এক রদ্দায় আমার ঘুম ছুটিয়ে দিতেন। তাই তো?
পারতেন না মশাই। স্থিরতা আর গতি একসঙ্গে যাপন করা যায় না। আমি যেমন ইচ্ছে থাকলেও আমার মায়ের শ্রমক্লান্ত হাতের তালুতে গাল রেখে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি না, তেমনই আপনিও নড়েচড়ে আমায় রদ্দা, কিল, ঘুষি, চড়, এমনকী, টোকাও মারতে পারেন না।
চেয়ার : তোমার সাহস তো কম নয় এরকম অপমান…
ঠিক এই সময়ে প্রেক্ষাগৃহের একদম পিছনদিকের দরজায় সামান্য, কিন্তু হৃদয়বিদারক একটা আওয়াজ হল। এক সেকেন্ডে আমার চলে যাওয়া ভয়টা ঝুপ করে আবার আমার ঘাড়ের কাছে এসে বসল। ভয়টাকে সামাল দেওয়ার আগেই চেয়ার বলে উঠল,
চেয়ার : এই সব্বোনাশ করেছে! কথায় কথায় খেয়ালই করিনি সময়ের কথা, এসে পড়েছেন, তুমি এবার কাটো, সাজঘর থেকে কী নেওয়ার আছে চট করে নিয়ে কেটে পড়ো, উনি এসে তোমাকে দেখলে কেলেঙ্কারি হবে। যাও, যাও, যাও…
আজ্ঞাপালনে দু-পা এগিয়েও খানিক থেমে চেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম…
আমি : আচ্ছা, কে আসছেন?
চেয়ার : খুব কৌতূহল না!
আমি : একটু তো হচ্ছেই…
চেয়ার : তাহলে চট্ করে একটা পক্ষ বাছো।
আমি : কীসের পক্ষ?
চেয়ার : বলো, তুমি স্থিরতার পক্ষে নাকি দৌড়ের? চটপট বলো…
উত্তরের আশায় আমার মস্তিষ্ক ‘স্থিরতা’ বলতে চাইলেও আমার ভবিতব্য ফস করে বলে ফেলল দৌড়ের পক্ষে।
চেয়ার : ব্যস, হয়ে গেল। যাও ফোটো, বলব না, দাঁড়িয়ে থেকো না। যিনি আসছেন, তাঁকে সহ্য করতে পারবে না, তোমার ক্ষমতার মধ্যে নয়। তোমাদের পরিচালক হলে চান্স ছিল।
ফিরিয়া পাইলাম অমূল্য রতন
তাড়াতাড়ি করে গ্রিনরুমে ঢুকে আলো জ্বালাতেই দেওয়ালে শবদেহের মতো ঝুলতে থাকা আয়নার সারি আত্মপ্রকাশ করল। মেগালোম্যানিয়া-বশত এই ঘুম-চোখেও একবার নিজের শবটা দেখে নিলাম। দেখতে পেলাম, ইমেজ-বিরোধী সেই ব্রণটাকেও, যা তিনদিন ধরে আমার ডানগালে রাজত্ব পাকাচ্ছে।
নিজেকে দেখতে আরও খানিক মশগুল হয়ে পড়তাম, যদি না তিন নম্বর আয়নাটা আমায় ডাকত।
৩ নং আয়না : এই যে হিরো, এতক্ষণে মনে পড়েছে? এদিকে এসো। আমার তলার ড্রয়ারে আছে তোমার মহামূল্যবান সম্পদ-দু’টি। পাহারা দিয়ে দিয়ে আগলে রেখেছি। তুমি শুধু পরেরদিন সঞ্জয়কে আমার সামনে সজ্জার পসরাটা সাজাতে বলো, তাহলেই কৃতার্থ হব। এই বইটার হিরোইনগুলো যা সুন্দর, মুখোমুখি দেখতে সাধ হয়।
আমি আয়নাকে আশ্বস্ত করে এবং আয়নার উদ্দেশে ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলে ড্রয়ার খুলেই পেয়ে গেলাম, যা নিতে এসেছিলাম। ভুল করে ফেলে যাওয়া এগারো হাজার টাকার অ্যানড্রয়েড ফোন ও দিনদুয়েক আগে উপহার পাওয়া জিপো-র লাইটার পকেটে ঢুকিয়ে আমি আবার মঞ্চ পেরনোর জন্য ঝাঁপাতে গেলাম। এবারে মায়নদী একসাঁতারে পার হতে হবে। বুকটা ঢিপঢিপ করছে।
প্রস্থান
খুবই দ্রুত মঞ্চ পেরলাম, ঘাড়ও ঘোরাইনি, তবু আড়চোখ বলে একটা বেয়াড়া দৃষ্টি আছে। তাতে বুঝলাম বাক্যবাগীশ চেয়ারকাকুর পাশের চেয়ারটিতে শুভ্র পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এক সুপুরুষ বসে, মাথার পিছনদিকের চুল ঝাঁকড়া। অসীম সামন্তর বইয়ে আমি এই ভদ্রলোকের ছবিগুলি খুঁটিয়ে দেখেছিলাম। আমার আড়চোখ ভুল দেখেনি। মঞ্চের ডানদিকে এসে দু-পাল্লার দরজাটা ঠেলা মেরে বেরনোর সময় শুধু একটা কথাই আমার কানে এসেছিল…
—শংকর, একটু চা খাওয়া না রে…
যে পথে ঢুকেছিলাম, সেই পথেই বাইরে বেরিয়ে এসে পুনরায় রেলিং টপকে ফুটপাতে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকারের ভেতর থেকে কেমন যেন একটা আলো-আলো ভাব নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। পুবদিকে তাকালাম। আকাশে খুব হালকা গোলাপি আর নীলচে রং-এর একটা আলো একে-অপরকে আদর করছে। ‘আত্মধ্বংসের আলো’।
এ-আলো আমি চিনতে পারলাম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, আমার ঘুম আরও গাঢ় হয়ে এল, চোখ ডলতে ডলতে আমি উবের ডাকলাম।
গাড়িতে উঠেই আমি বেহায়া ঘুমের কবলে চলে গেছিলাম। ড্রাইভারদাদার ডাকেই ঘুম ভাঙল ডেস্টিনেশনে।
গাড়িতে ওঠার সময় খেয়াল করিনি, বাড়ির সামনে নেমে লক্ষ করলাম— এই বিশেষ উবেরটিতে নম্বর প্লেট নেই।
১. ‘অদ্য শেষ রজনী’-র নির্দেশক ব্রাত্য বসু
২. ‘অদ্য শেষ রজনী’-র আলোকশিল্পী সুদীপ সান্যাল
৩ ‘অদ্য শেষ রজনী’-র রূপসজ্জা শিল্পী সঞ্জয় পাল
৪. শংকর চক্রবর্তী— চতুর্মুখ নাট্যদলের গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা ও সদস্য
***শুভ্র পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সুপুরুষ ভদ্রলোক… এটা বলব না।
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি:
এই গদ্যটি লেখা হয়েছিল ১ নভেম্বর, ২০১৬। ব্রাত্য বসু নির্দেশিত ‘অদ্য শেষ রজনী’-র মঞ্চায়ন তখনও চলছে। এখন আর নাটকটি অভিনীত হয় না।পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook