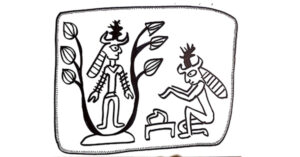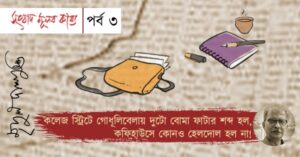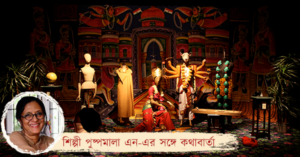মাস পয়লা, পাড়ার ব্যাংকের সামনে ভিড় সেই সকাল সাড়ে ন-টা থেকেই। এই দিন পেনশনের টাকা আসে। হরিপ্রসন্ন পুরকায়েত লাঠি ঠুকঠুক করে এসে বসলেন সরকারি ব্যাংকটার বাইরে গাছের ছায়ায়। আরও পাঁচজন তাঁরই মতো এসেছেন, যেমন আসেন প্রত্যেক মাসের শুরুতে। মাথায় করে সব্বাই নিয়ে আসেন একটাই ভাবনা— কীভাবে জীবন কাটবে এই দুর্মূল্যের বাজারে। খুব হতাশা নিয়ে তিনি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকেন তাঁর ভবিষ্যতের কথা! দুষতে থাকেন দেশের অর্থনীতিকে, সরকারকে।
আসলে হরিপ্রসন্নের দুর্ভাবনা শুধু তাঁর একার নয়, আমাদের অনেকের ভাবনার সঙ্গেই তা মেলে আজকাল। একদিকে পড়ন্ত সুদের হারে পর্যুদস্ত আমরা কমবেশি সকলেই । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি। সঙ্গে অতিমারি এবং তার পরবর্তী সময়ের ভয়াবহতা। সব মিলিয়ে নাভিশ্বাস ব্যাংক-গ্রাহকদের। ব্যাংকিং ব্যবস্থাও কি খুব সুখে আছে? তা-ও নয়। কারণ একটা জিনিস বুঝতে হবে, গ্রাহক এবং ব্যাংকের মধ্যের যোগাযোগের সূত্র কিন্তু একটাই― সেটা হল অর্থসম্পদ। অর্থাৎ গ্রাহক হিসেবে সুদের বিনিময়ে আমরা আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ গচ্ছিত রাখি ব্যাংকের কাছে। ব্যাংক সেই টাকা লগ্নি করে কোনও ঋণপত্রে অথবা অন্য কোনও ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেয় নির্দিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের জন্য। এর থেকে সুদ হিসেবে যা আয় হয় ব্যাংকের, তারই একটা অংশ ফেরত আসে গ্রাহকের কাছে। গোলমালটা বাধে যে-পরিমাণ অর্থের চাহিদা এবং জোগান আছে এই মুহূর্তে বাজারে, তার মধ্যে অসামাঞ্জস্য হলে।
ব্যাংকের সংজ্ঞা হিসেবে যা আমরা সাধারণত জেনে এসেছি তা হল, ‘ব্যাংক আমানত গ্রহণ এবং ঋণ দেওয়ার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান’। মহাজনী ব্যবসার সঙ্গে এই তার প্রভেদ যে, মহাজন নিজের টাকা খাটান, ব্যাংক খাটায় অন্যের গচ্ছিত রাখা টাকা। সুতরাং পুরকায়েতবাবুর কথা একশো ভাগ ঠিক। আধুনিককালে ব্যাংকের বিবিধ ভূমিকা যাই হোক না কেন, এটাই হল তার গঠনতন্ত্রের মূলসূত্র। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। ১৯২৭ নাগাদ তোড়জোড় শুরু হলেও আইনি প্রক্রিয়া কাটিয়ে ১৯৩৫ সালে কাজ আরম্ভ করে রিজার্ভ ব্যাংক। এই তো কয়েক বছর আগেকার কথা, দেশের চারটে সরকারি ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অফিস ছিল কলকাতার ঠিকানায়। পরিবর্তনের চাপে সেসব এখন অতীত। এখন রয়ে গেছে একটিমাত্র বেসরকারি ব্যাংক, এক বাঙালি শিল্পোদ্যোগীর হাত ধরে।
মুঘল সাম্রাজ্যের সময় থেকে দেশজ ব্যাংকিংয়ের একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। সম্রাট আকবর-এর সময়ে (‘আইন-ই-আকবরি’ অনুসারে) দেশের অনেকগুলো টাঁকশাল বন্ধ হয়ে যায়। চারটি বড় টাঁকশালে আগ্রা, লখনউ, আহমেদাবাদ এবং কাবুলে সোনার মোহর তৈরি হতে থাকে। তামা আর রুপোর মুদ্রা তৈরির কাজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এই চারটি কেন্দ্র ছাড়াও আরও দশটি শহরে। আরেকটা জিনিসও গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল এই সময় থেকেই মুদ্রার নকশা ও নির্মাণ পদ্ধতিতে আসে নতুনত্ব। ঔরংজেবের সময়ে আরও উন্নত হয় মুদ্রার নকশা; কবিতার অংশ, ক্যালিগ্রাফি, রাশিচক্রের ছবি― সব মিলিয়ে এক উচ্চমার্গে পৌঁছে যায় মুঘলমুদ্রা।
এবার জগৎশেঠের কথায় আসি। ১৬৯৫ সাল। রাজস্থানের যোধপুর থেকে জৈন পরিবারের এক মাড়োয়ারি পুরুষ এসে পটনায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মানিকচাঁদ বাংলার শাসক মুর্শিদকুলির ব্যাংকার ছিলেন এবং দিল্লিতে বাদশাহ ঔরংজেবের কাছে বাংলার রাজস্ব তাঁর মারফত পাঠানো হত। তাঁর কাজেকম্মে বাদশাহ বেজায় খুশি হয়ে ১৭১৫-তে তাঁকে উপাধি দিলেন ‘শেঠ’। মানিকচাঁদ শেঠের ভাইপো ফতেচাঁদ এই ব্যবসার উত্তরসূরি। নবম মুঘল বাদশাহ ফারুখশিয়ারকে সিংহাসন লাভের সময়ে তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। জগৎ শেঠের পরিবারের ব্যাংকিং ব্যবসা বেশ ফুলেফেঁপে উঠল। ফতেচাঁদের নাতি মাহতাপচাঁদের সময়ে তা পৌঁছল উন্নতির শিখরে। শেঠ পরিবারের কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে এরকম কোনও ব্যাংকার তখন নেই ভারতে। আর বাংলাদেশে তো তাদেরই প্রতিপত্তি; ছোট-বড় সব আঞ্চলিক ব্যাংকার হয় শেঠ পরিবারভুক্ত বা তাদের প্রতিনিধি! জগৎশেঠের ঐশ্বর্যের কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না।
দেশীয় ব্যাংকারদের শ্রেণিবিভাগ ছিল, যার বেশিটাই নির্ভর করত তার মূলধন, ঋণ দেবার ক্ষমতা আর পরিষেবার রকমফের হিসেবে। রাজা বল্লাল সেনের সময়ে নাকি সুবর্ণ বণিকরা ব্যাংকিং চালাত। এরপর মুসলিম শাসনকালে,ব্যবসাবাণিজ্য বেড়ে যেতে, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম থেকে দেশীয় ব্যাংকাররা এসে ভিড় করে বঙ্গে। মনে রাখতে হবে ভৌগোলিকভাবে নদী ও সমুদ্রের কাছে অবস্থিতি হবার কারণে দেশীয় ও বৈদেশিক লেনদেনের কেন্দ্র ছিল এই বাংলা। ‘কুঠিওয়ালা’ প্রকৃত ব্যাংকার আর ‘পোদ্দার’ (বা ‘শ্রফ’), তারা বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশের মুদ্রাবিনিময়কারী, মানে আজকের মানিচেঞ্জার।
জগৎশেঠের ব্যবসা তখন তরতর করে বেড়ে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য বড়-বড় শহরেও পৌঁছেছে। গয়া আর দাউদনগরে ছিল আরেক শ্রেণির ব্যাংকার, যাদের বলা হত ‘আড়তদার’। এদের প্রধান কাজ ছিল হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো। গয়া থেকে পটনাতে টাকা পাঠানোর কমিশন ছিল শতকরা চার আনা আর কাশীতে আট আনা! এ ছাড়াও আরও ছোট-ছোট কিছু দেশজ ব্যাংকার ছিল― ‘নুকুড়িমহাজন’, কোথাও বা ‘সাহুমহাজন’। এ-প্রসঙ্গে হয়তো বা মনে পড়বে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’-এর ধাওতাল সাহুকে!
যেটা লক্ষণীয়, সেটা হল, সেকালের ব্যাংকিং পরিষেবাও মূলত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে রাজন্যবর্গ, বণিকশ্রেণি এবং ধনী মানুষদের প্রয়োজনকে সামনে রেখে। বাদশাহ, নবাব, আমির, ওমরাহকে টাকা ধার দেওয়া আর হুন্ডির মাধ্যমে রাজস্ব পাঠানো রাজকোষে― এই দুই ছিল ব্যাংকারদের প্রধান কাজ। কিন্তু এ-রাস্তা ধরেই আস্তে-আস্তে বেনিয়মের ঘোলাজল ঢুকতে শুরু করল ব্যাংক ব্যবসায়। এক সময়ে অর্থের পরিবর্তে শস্যের বিনিময়ে রাজস্ব দেওয়া যেত। পরে এই নিয়ম বন্ধ হলেও, অনেক সময়ে দেখা যেত নির্দিষ্ট দিনে খাজনা আদায় না হলে জমিদার বা ভূস্বামীদের টাকা ধার করতে হত কুঠিওয়ালাদের থেকে রাজস্ব জোগাড়ের জন্য। সেই ধারকার্য হত শস্য বন্ধক রেখে। অতএব ব্যাংকদের সমান্তরালভাবে শস্যের ব্যবসা না করলে চলত না। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষের দিকে ডামাডোলের বাজারে দেশীয় ব্যাংকারদের কাছে টাকাপয়সা আমানত রাখার পরিমাণ বেড়ে যেতে তারা এই টাকা খাটাতে শুরু করল নিজেদের শস্য বা অন্যান্য ব্যবসায়। যেহেতু রাজস্ব পাঠানো ছিল ষান্মাসিক বা বাৎসরিক ঘটনা, সুতরাং বাকি সময়ের গদির খরচ তোলার জন্য তারা গ্রাহকের গচ্ছিত টাকা নিজেদের অন্য ব্যবসায় খাটাতে শুরু করল অসাধু উপায়ে। পরবর্তীকালে দেখা যাবে, ঠিক এই কারণে বাংলা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকিং কোম্পানি দেউলিয়া হতে বসেছিল।
বাংলার ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ নগরের কথা এসেই পড়ে। মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে নবাবি এবং ব্রিটিশ আমলের প্রচুর ঝড়ঝাপটা গেছে। কিন্তু কালান্তরে সে নগর হয়ে উঠেছিল ব্যবসাবাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা ও বিনিময়ের এক প্রধান কেন্দ্র। ‘রিয়াস-উল-সালাতিন’, ব্রিটিশ সময়কালের মুসলিম নবাবদের নিয়ে লেখা বইটি বেরিয়েছিল ১৭৮৮ নাগাদ। সে-বই জানান দিচ্ছে যে মুখসুদ খাঁ নামে এক ব্যবসায়ীর নামে ভাগীরথী তীরের এই ছোট্ট নগরের নাম হয়েছিল মুখসুদাবাদ। বঙ্গদেশে পটনা (আজিমাবাদ), ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) আর রাজমহল-এ তখন তিনটে বড়-বড় টাঁকশাল। জগৎশেঠ মানিকচাঁদের পরামর্শে তৈরি হল আর একটা টাঁকশাল মুখসুদাবাদে। সময়টা সম্ভবত ১৭০৪ বা ১৭০৬ সাল। আগেই বলেছি, ঔরংজেবের সময়ে আরও উন্নত হয় মুদ্রার নকশা। তাঁর আমলে হিজরি ১১১৬ শাসন বর্ষে (১৭০৪ সাল) দু-রকম মুদ্রা পাওয়া গেছে― একটির গায়ে ‘মুখসুদাবাদ’ খোদাই করা, অন্যটির গায়ে মুর্শিদাবাদ। ১৭০০ সালে ঔরংজেব করতলব খাঁ-কে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময়ে বাংলার সুবেদার ছিলেন তাঁর নাতি আজিম উস সান। রাজস্ব বাড়াবার এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি হিসেবে প্রথমেই করতলব তাঁর দিওয়ানখানা সরিয়ে নিয়ে এলেন জাহাঙ্গীরনগর থেকে মুখসুদাবাদে। শুরু হল আজিম উস সান-এর সঙ্গে বিবাদ। রাজস্ব বাড়ল, নবাব খুশি হলেন, ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে করতলব খাঁ উপাধি পেলেন মুরশিদকুলি খাঁ! নিজের নামে সাধের নগরের নাম রাখলেন মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের গা ঘেঁষে কাশিমবাজারে ব্রিটিশদের বাণিজ্যকুঠি; রেশমের কেনাবেচা, রফতানি হয় সেখান থেকে। বাংলা থেকে রফতানি আর বাংলায় আমদানি― এই দুয়ের পর বাংলা থাকত উদ্বৃত্ত (surplus balance of trade)। ফলত ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা ধরনের মুদ্রা এসে জমা হত বাংলায়, যার মূল্য মান সমতুল নয় (not standardised)। ইতিহাস বলছে সে-সময়ে প্রায় ৩২ ধরনের মুদ্রার চল ছিল বাংলা জুড়ে। সাহেবরাও নবাবের অনুমতি নিয়ে তৈরি করত মুদ্রা। প্রতিটি মুদ্রার বিনিময় হার ঠিক করতে হত, যে-কাজটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে করত জগৎশেঠের পরিবার। মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের তত্ত্বাবধায়ক বা দারোগা ছিল রঘুনন্দন। তার মৃত্যুর পর টাঁকশালের পূর্ণ অধিকার চলে আসে শেঠ-পরিবারের হাতে।
১৭৩৭ সালে বাংলার ডেপুটি দেওয়ান আলমচাঁদ ইংরেজদের বললেন, গত পাঁচ বছরের বাংলায় আনা সোনা-রুপোর হিসেব দাখিল করতে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো। নিরুপায় হয়ে ইংরেজরা মাদ্রাজি টাকা আনা কমিয়ে ফেলে আবার বাংলায় সোনা-রুপো আমদানি শুরু করল ।
এরপরেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জাঁকিয়ে বসে কলকাতায়। দুর্গ তৈরি করে তারা। ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ-দৌলা প্রথম রাউন্ডে কলকাতা আক্রমণ করে জিতে গিয়ে সে-শহরের নাম রাখেন ‘আলিনগর’। সে-সময়ে কলকাতার টাঁকশালে নবাবি মুদ্রা ছাপা হত ‘আলিনগর কলকত্তা’ এই নামে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা পুনর্দখল করে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করলে টাঁকশালের নাম পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায় ‘কলকত্তা’। মোটামুটি ভাবে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ অবধি বজায় ছিল মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের গরিমা বা সে-অর্থে মুর্শিদাবাদ নগরের গুরুত্ব। শুরু হল কলকাতা শহরকেন্দ্রিক ইংরেজ শাসনব্যবস্থা― ‘বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে’!
যুদ্ধে জিতে কলকাতার ইংরেজ কেল্লা দখল করলেও পরবর্তী সময়ে সিরাজ-উদ-দৌলাকে ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের চুক্তি সই করতে হয় এবং তার শর্ত হিসেবেই ইংরেজরা কলকাতার টাঁকশালে মুদ্রা উৎপাদনের অনুমতি পেয়ে যায় । ১৭৫৯-’৬০ সালে কলকাতায় প্রথম টাঁকশালটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে এই টাঁকশালের নাম ছিল ‘ক্যালকাটা মিন্ট’। তবে এই টাঁকশালটি ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায় না। এর পরের কয়েক বছর টানাপোড়েন চলতে থাকে কলকাতা কাউন্সিলের সঙ্গে শেঠ-পরিবারের। কারণ কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে মুদ্রা তৈরি হলেও, শেঠ-পরিবারের কর্তৃত্ব তখনও বজায় আছে বাংলার মুদ্রাব্যবস্থায়। অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ১৭৬০-এ, ইংরেজ বশংবদ নবাব মীরকাশিমের পরোয়ানায়। মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কলকাতার মুদ্রার উপর বাট্টা বা প্রিমিয়াম নেওয়া নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হল। এভাবেই শেষ পেরেক পোঁতা হল নবাবি টাঁকশালের ওপর। ১৭৮৫-তে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একবার চেষ্টা হলেও ইংরেজদের চাপে তা আর সম্ভব হল না। বাংলার ব্যাংকিং বাস্তবিক ভাবেই এক নতুন মোড় নিল ।
এবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি মাঠে নামে। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৭ সালে গঠন করেন এক কারেন্সি কমিটি। কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারের (exchange rate) মধ্যে এক ধরনের সমতা ও সমন্বয় সাধন। ১৭৯০ সাল নাগাদ বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি এনে তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় ক্যালকাটা মিন্ট। দ্বিতীয় টাঁকশাল থেকেও মুর্শিদাবাদের নামে মুদ্রা উৎপাদিত হত। ১৮২৪ সালের মার্চ মাসে তৃতীয় টাঁকশালের শিলান্যাস করা হয়। এই টাঁকশালটি চালু হয় ১৮২৯ সালের ১ অগস্ট। ১৮৩৫ সাল অবধি এই টাঁকশাল থেকে মুর্শিদাবাদের নামে মুদ্রা উৎপাদিত হত। স্ট্র্যান্ড রোড আর পোস্তাবাজারের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই টাঁকশালটির নাম ছিল ‘ওল্ড সিলভার মিন্ট’। ১৮৬০ সালে এই টাঁকশালের উত্তরে কেবলমাত্র তাম্রমুদ্রা উৎপাদনের জন্য কপার মিন্ট নামে আর একটি ভবন সংযোজিত হয়।
যে-ব্রিটিশ সওদাগরি ফার্মগুলো কলকাতায় তাদের অফিস তৈরি করেছে, তারাই ব্যবসার পথ সুপ্রসারিত করতে ঢুকে পড়েছিল ব্যাংকিং ব্যবসায়। এরা অধিকাংশই ছিল agency house। সাধারণ এবং সামরিক সরবরাহ, পাট, নীল, রেশম, মশলা, চা, লবণ ইত্যাদির দালালি, উত্তর ভারতের নানা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা ব্যবসাদারদের প্রতিনিধি এসবই ছিল এদের অধীনে। পাশাপাশি দেশীয় মালিকানায় শুরু হয়েছিল বেশ কিছু ব্যাংক। ১৭৭০-এ ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান কাজকর্ম শুরু করে। আলেক্সান্দার অ্যান্ড কোম্পানি ছিল এর মালিক। ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান প্রথম কাগজের নোট ছাড়ে বাজারে কিন্তু তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল শহর কলকাতা ও তার আশেপাশেই সীমাবদ্ধ। সে ভাবে তা ‘legal tender’ বলে স্বীকৃত হয়নি। কলকাতা এক্সচেঞ্জ লটারি-র এজেন্ট ছিল এই ব্যাংক। ১৭৯০ থেকে ১৮০০-র মধ্যে চালু ছিল বেঙ্গল ব্যাংক। এদের ব্যাংক নোটেরও খুব একটা প্রচলন ছিল না। পাশাপাশি ছিল জেনারেল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ১৭৯১ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তৈরি হল কারনাটিক বা কন্নর ব্যাঙ্ক। ব্যাংক অফ ক্যালকাটা-র পথচলা শুরু হয়েছিল ১৮০৬ সালের ১ মে। এখানে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয়; বম্বে, যা পরবর্তী কালে ভারতের অন্যতম শিল্প ও বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে খ্যাতিলাভ করবে, সেখানে কিন্তু ১৮৪০-এর আগে কোনও ব্যাংক স্থাপিত ছিল না।
১৮০৯ থেকে ১৮৩৯-এর সময়কালে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যাংকের অনেক পরিবর্তন দেখা যায় কালক্রমে। কমার্শিয়াল ব্যাংক, কলকাতা ব্যাংক, আগ্রা অ্যান্ড ইউনাইটেড সার্ভিস ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গভর্নমেন্ট সেভিংস ব্যাংক, শ্রীরামপুর সেভিংস ব্যাংক এবং মির্জাপুর ব্যাংক অস্তিত্ব লাভ করে। ১৮২৯ সালে কলকাতা ব্যাংক ফেল করে। সে-সময়ে এজেন্সি হাউস এবং ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ ছিল নীল ব্যবসায়। ১৮২৫ থেকে সেই ব্যবসায় দেখা দিল মন্দা। ১৮৩২ নাগাদ নীলের দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ১৮২৫য়ে অ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধ ও ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা। ১৮৩২ থেকে শুরু হয় ভাঙার খেলা । ১৭৭০ সাল থেকে চলে আসা ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান, কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং কয়েকটি ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান এই ভয়াবহ সংকটে পড়ে। মির্জাপুর ব্যাংক ১৮৩৭ সালে জন্মের দুই বছর পর ভেঙে পড়ে। ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান পরে পুনরুজ্জীবিত হলেও, দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হয় ১৮৬৬ সালে।
ঠিক এরকম সময়ে দেশের দক্ষিণে ও পশ্চিমে জন্মলাভ করে দুটি নতুন ব্যাংক― ব্যাংক অফ মাদ্রাজ ৩০ লক্ষ সিক্কা টাকা ও ব্যাংক অফ বম্বে ৫০ লক্ষ সিক্কা টাকা মূলধন নিয়ে কাজ শুরু করে যথাক্রমে ১৮৪৩ ও ১৮৪০ সালে ।
ব্যাংক অফ বেঙ্গল, ব্যাংক অফ বম্বে ও ব্যাংক অফ মাদ্রাজ― এই তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংকের গুরুত্ব, ভবিষ্যতের ভারতীয় ব্যাংকিংয়ের সামগ্রিক যে-রূপরেখা, তার পরিপ্রেক্ষিতে অপরিসীম। সুতরাং এদের কথা একটু বিশদে বলা দরকার। কিন্তু তার আগে একবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ঘুরে যেতে হবে।
পরিবারের কর্তা রামলোচন অপুত্রক। তাঁর জীবনাবসানে বিশাল জমিদারির দায়িত্ব পড়ল দত্তক পুত্র দ্বারকানাথের উপরে। কতই বা বয়েস হবে তাঁর সে-সময়ে! বড়জোর তেরো। এরপর প্রায় চার দশক ধরে চলল তাঁর নানা ধরনের ব্যবসায়িক অভিযান। সেদিনের সেই নাবালক হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। দেশে তো বটেই, ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তৈরি হল সখ্য। পৈতৃক জমিদারির দেখভাল করে আয়েশের জীবন কাটিয়ে দেবার বাসনা ছিল না তাঁর। শুরু করলেন ব্যবসা। পাট, সিল্ক, মশলা, নীল, কয়লা, চা, নৌ-পরিবহন, এসব ব্যবসার হাত ধরে গড়ে ওঠে তাঁর সাম্রাজ্য, যার আয় জমিদারির রাজস্বের থেকেও বেশি। ব্যবসা প্রসারের জন্য দরকার ব্যাংকিং পরিষেবা। কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলার ব্যাংকিংয়ের নিতান্তই শৈশব অবস্থা। ব্যাংক অফ বেঙ্গল, ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান, ক্যালকাটা ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে প্রথমটি আধা-সরকারি ব্যাংক, যা একপ্রকার কোম্পানি বাহাদুরের খাজাঞ্চিখানা। অপর তিনটি ব্যাংক কোনও-না-কোনও কুঠি বা কারবারের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ, সেই কুঠির স্বার্থরক্ষাই তাদের মূলধর্ম। পাবলিক ব্যাংক বলতে আমরা যা বুঝি, সেই অর্থে, টাকাপয়সা লেনদেনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে এদের দরজা উন্মুক্ত ছিল না । দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন ব্যাংক যদি কেবল কোনও কুঠি বা কারবারের অংশবিশেষ অথবা কোম্পানি বাহাদুরের খাজাঞ্চিখানা হয়, তবে তা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যকে সামগ্রিক ভাবে মদত জোগাতে পারবে না । ১৮২৮ সালে শুরু হল ইউনিয়ন ব্যাংক (বর্তমান ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই) তৈরির কাজ, যার কর্মকাণ্ড চালু হয় হয়েছিল ১৮২৯ সালে। সে-সময়ে দ্বারকানাথ ছিলেন কোম্পানির কাস্টমস অফ সল্ট অ্যান্ড ওপিয়াম বোর্ডের দেওয়ান পদে। যার ফলে তাঁর নাম প্রথম দিকে প্রকাশ্যে আনা যায়নি ব্যাংকের মালিক হিসেবে। কিন্তু মূলধন হিসেবে একটা মোটা টাকা এসেছিল তাঁর পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং আশ্রিতদের নামে কেনা শেয়ার থেকে। বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুর এবং প্রিয় বন্ধু উইলিয়াম কার নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ ও সেক্রেটারি হিসেবে। এই উইলিয়াম কার সাহেবই পরবর্তীকালে দ্বারকানাথের ব্যবসার অংশীদার হন এবং দুজনে মিলে তৈরি করেন Carr, Tagore and Company । যেটা বলার বিষয়, ১৮২৮-’২৯ থেকে শুরু করে পরের প্রায় কুড়ি বছর ইউনিয়ন ব্যাংককে কেন্দ্র করে কলকাতা ও বাংলা জুড়ে গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যের এক বিশাল ইমারত আর সেই কৃতিত্বের দাবিদার অবশ্যই প্রিন্স দ্বারকানাথ। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩― অর্থনৈতিক মন্দার কালেও এই প্রতিষ্ঠানের গায়ে আঁচড় লাগতে দেননি তিনি; বরং যেটা করেছিলেন, সেটা আজকের যুগে আমরা ‘financial bail out’- এর তকমা লাগিয়েছি। কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রোমোটার মাকেনটস অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবংশের ছেলে গোপীমোহন ঠাকুর এবং বন্ধু, রাজা রামমোহনের সূত্রে। ব্যাংকের অংশীদারও হয়েছিলেন। ১৮৩২ সালে যখন সেই ব্যাংক ফেল করে, দ্বারকানাথ ঘোষণা করেন তাঁর ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংকের সমস্ত ব্যাংক নোট এবং অনান্য দেনা পরিশোধ করবে এবং যত টাকা বাজারে পাওনা আছে, তা-ও আদায় করবে।
এভাবেই এক ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যাংকিং ও বাণিজ্য ব্যবস্থাকে দৃঢ় হাতে টেনে তোলার যে চেষ্টা দ্বারকানাথ করে গেছিলেন সে-সময়ে, তা বাঙালির ব্যাংকিং ইতিহাসের মাইলস্টোন!
১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ-পরবর্তী সময়ে দেশের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে গেল। সেইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও মুদ্রাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য ভাইসরয় কাউন্সিলের পনেরোজন সদস্যের মধ্যে একজন Financial Member মনোনীত হলেন। জেমস উইলসন ছিলেন প্রথম Financial Member, যিনি বুঝেছিলেন প্রাদেশিক ব্যাংকিংয়ের ভিতের ওপর গড়ে তুলতে হবে একটি জাতীয় ব্যাংকিং কোম্পানি। এর মধ্যে গোল বাধাল ব্যাংক অফ বম্বে ! ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে দু-দু’বার দেউলিয়া হতে হল বাজারে অনাদায়ী ঋণের দায়ে। আর এখানেও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল ব্যাংক অফ বেঙ্গল, কারণ সে-সময়ে ব্যাংক অফ বম্বে ছিল পশ্চিমদেশে তার এজেন্ট। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে ব্যাংক অফ বেঙ্গলের ডিরেক্টররা এবার মাঠে নামলেন; কোষাধ্যক্ষ ও সেক্রেটারি ডিকসন সাহেব সরকার বাহাদুরের কাছে পেশ করলেন বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ব্যাংক-এর সংযুক্তিকরণের প্রথম পরিকল্পনা। পাঁচ কোটি সিক্কা টাকার মূলধন নিয়ে শুরু হবে এই ব্যাংক, যার কেন্দ্রীয় বোর্ড হবে কলকাতায় এবং সেখান থেকেই বাকি দুটো ব্যাংকের কাজকম্মের নির্দেশ দেওয়া হবে। তবে দুই শহরেই থাকবে স্থানীয় বোর্ড।
ব্যাংক অফ বোম্বে এবং মাদ্রাজের ডিরেক্টররা সম্মতি দিলেও বাদ সাধলেন ব্যাংক অফ বেঙ্গল-এর শেয়ারহোলডাররা। আর এই সুযোগে ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স জল ঢেলে দিলেন সেই পরিকল্পনায়, তাঁর বরাবরই ভয় ছিল এই সংযুক্ত ব্যাংকিং সংস্থা কালক্রমে এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে, সেটি হয়তো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যাবার দাবি জানাবে কোনও একদিন।
এভাবেই শেষ হয়ে গেল কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং সংস্থায় বাংলার শীর্ষস্থান অধিকারের প্রথম পদক্ষেপ! ১৮৯৯ থেকে ১৯০১― এরকম সময় জুড়ে ইংরেজ সরকার বাহাদুর, প্রাদেশিক সরকার, ব্যবসায়ী মহল এবং চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংযুক্তিকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে মতবিনিময় হয়। যেটা পরিষ্কার হয়ে যায় তা হল, সে-সময়ে ব্যবসার জন্য যে-ধরনের আর্থিক সহায়তা (bank credit) দেশে প্রয়োজন, তা অপ্রতুল। অর্থাৎ দেশে মূলধন বা পুঁজির জোগান বাড়ানো প্রয়োজন এবং সেই বৃদ্ধির জন্য যে-মাপের আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তা একমাত্র তিনটি ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমেই সম্ভবপর। বম্বে চেম্বার অফ কমার্স এবং বাংলার লেফট্যানেন্ট গভর্নরের বক্তব্য থেকে বোঝা গেল সেই ব্যাংকের পরিচালনা নিয়েই সবাই চিন্তিত ও সন্দিহান।
১৯০০-১৯০১ সালে স্যার এডওয়ার্ড ল, তৎকালীন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী, প্রেসিডেন্সি ব্যাংক, মুদ্রা-বিনিময় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, প্রাদেশিক সরকার এদের সঙ্গে আরেক প্রস্থ আলোচনা সেরে যে-রিপোর্ট দেন, তা মোটামুটি এই রকম―
‘the conclusions which have forced themselves on my mind are that there is under present conditions no real necessity for the foundation of such a bank in the interests of trade, and that although, in my opinion, the existence of a strong bank with abundant resources would be useful in connection with possible exchange difficulties… from other points of view, be convenient to Government, the direct cost of its establishment would be greater than I venture to recommend for acceptance. I am still of opinion that if practical difficulties could be overcome, it would be distinctly advisable to establish such a bank so as to relieve Government of present heavy responsibilities and to secure the advantages arising from the control of the banking system of a country, by a solid, powerful, Central Institution…’
লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস তখন ভারতজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনক্ষমতা ইংরেজ সরকার বাহাদুরের কাছে হস্তান্তর হওয়ার পর থেকেই এই বিভাগটি চালু হয় একজন সেক্রেটারি অফ স্টেটের তত্ত্বাবধানে। ১৯০১-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে সেক্রেটারি অফ স্টেট সাময়িক ভাবে এই পরিকল্পনা বন্ধ রাখেন।
গণিতজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস ১৯০৬ সালে সিভিল সারভেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে। ১৯১৩ সালে যখন তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা দাখিল করতে, তিনি ‘Proposals for the establishment of a State Bank for India’ নামে রিপোর্টটি তুলে দেন সরকারের হাতে। বলা যেতে পারে এটিই হল সেই ঐতিহাসিক দলিল, যাকে ভিত্তি করে তৈরি হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাঠামো। নতুন ব্যাংকের নামকরণ হল ‘ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া’, যার ক্যাপিটাল ও রিজার্ভ আদতে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংকের সংযুক্ত রাশি, যেখানে সরকারের কোনও অংশীদারিত্ব নেই। ব্যাংক পরিচালনার ভার দেওয়া হল একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের ওপর, যার মাথায় থাকলেন ব্রিটিশ রাজা নিয়োজিত গভর্নর। ‘The Imperial Bank of India Bill’ ১৯২০-তে পাশ হয়। অবশেষে ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে শুরু হল ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র যাত্রা। যদিও ১৯২৪ সালে ইম্পেরিয়াল ব্যাংকের প্রধান দপ্তর নিয়ে যাওয়া হয় বম্বেতে, এর জন্মলগ্নে ব্যাংক অফ ক্যালকাটা ও পরে, ব্যাংক অফ বেঙ্গল-এর যোগদান ছিল তর্কাতীত।
কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন (১৯১৪ সালে নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত), বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক (১৯১৮ সালে জেসি দাস প্রতিষ্ঠিত), কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক (১৯২২ সালে ইন্দু ভূষণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত) এবং হুগলি ব্যাংক (১৯৩২ সালে ডি এন মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত)― এই চারটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক ব্যাংক হিসেবে বেশ কিছু সময়ে তৎকালীন বঙ্গদেশে কাজ করেছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এই ছোট ব্যাংকগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৫০ সালে, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক লিমিটেড (১৯১৮ সালে বেঙ্গল সেন্ট্রাল লোন কোম্পানি লিমিটেড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত) নামবদল করে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া করা হল; উদ্দেশ্য ওই চারটি ব্যাংককে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো।
১৯২০ সালে ইলাহাবাদ শহরে ইলাহাবাদ ব্যাংক-এর জন্ম। ১৯২৩ নাগাদ এই ব্যাংকের সদর দপ্তর কলকাতায় চলে আসে ব্যবসা প্রসারের কারণে। ১৯৪২ সালে ঐতিহাসিক ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের পর ভারতীয় শিল্প নবজাগরণের নায়ক জি ডি বিড়লা ১৯৪৩-এর ৬ জানুয়ারি, দ্য ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড স্থাপন করেন, যার হেড অফিস হয় কলকাতায়। এই তিনটি ব্যাংক, অর্থাৎ ইউনাইটেড ব্যাংক, ইলাহাবাদ ব্যাংক এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউকো ব্যাংক) ১৯৬৯-এর ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের সময়ে পাবলিক সেক্টর ব্যাংক হিসেবে পরিগণিত হয় আরও ১১টি ব্যাংকের সঙ্গে। কিন্তু এদেরও জীবন শেষ হয়ে যায় যখন ২০২০-র পয়লা এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ মেনে যথাক্রমে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক এবং কানাড়া ব্যাংক-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মধ্যে দিয়ে।
তথ্যঋণ:
- The History of The Bank of Bengal: An Epitome of 100 years of Banking in India by G P Symes Scutt
- দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ : কৃষ্ণ কৃপালানি, অনুবাদ: ক্ষিতীশ রায়
- RBI.org.in
- মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রবন্ধকার সুমন মিত্র/ সম্পাদক: অরিন্দম রায়