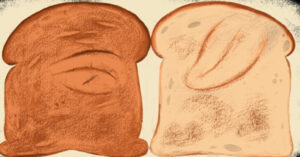ফিরে কখন দেখে লোকে? ফিরে কখন দেখে না, সেটা বরং ভাবা সোজা। যখন গন্তব্যপথ নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তা থাকে না, বা নিয়মিত চলাফেরার কক্ষপথে যাত্রাপথের সূচনাবিন্দুতে ইচ্ছেমতো ফিরে আসার সম্ভাবনা নিয়ে কোনও সংশয় থাকে না, তখন ফিরে দেখার দরকার কী? যেমন প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় কিছু ফেলে না এলে, প্রিয়জনকে বিদায় জানাতে না হলে, কেউ পিছু না ডাকলে বা অকস্মাৎ কিছু না ঘটলে ফিরে তাকানোর দরকার কী, বিশেষত যদি তাড়া থাকে? কথাই তো আছে, পিছু না ডাকতে। জনপ্রিয় সংস্কৃতিতেও এই একই ভাবনার রেশ, যেমন বব ডিলানকে নিয়ে বানানো তথ্যচিত্রের নাম ‘ডোন্ট লুক ব্যাক’, বা সাহির লুধিয়ানভীর লেখা জনপ্রিয় হিন্দি গানের কথা— ‘পিছে দেখে না কভি মুড়কে রাহো পে’।
তবে জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে ফিরে তাকাতেই হয়। তার মধ্যে কিছুটা স্মৃতিমেদুরতা আছে। যা হারিয়ে গেছে চিরতরে, তার জন্যে মায়া এবং বিষাদমাখা পিছুটান। তা শুধু মানুষজন, ফেলে আসা দেশ, শহর, পাড়া, বাড়ি, পরিচিত পথঘাট-দোকানপাটের জন্যে নয়, আমাদের কিছু অনুভূতির জন্যেও। শৈশব বা কৈশোরের একটা সংবেদনশীল ও কল্পনাময় জগৎ থাকে, আর থাকে চারপাশের সব কিছু নিয়ে সারল্যমাখা কৌতূহল ও উৎসাহ। কিন্তু বহির্জগতে কেন কী হয়, তা নিয়েও অনেক আপাতসরল প্রশ্ন ও চিন্তাভাবনা থাকে। যেমন, তার মধ্যে ক্রিসমাসে সান্টা ক্লস সত্যি মোজায় উপহার দিয়ে যান কি না আছে, আবার চায়ের দোকানে কাজ করা ছেলেটা স্কুলে যায় না কেন, এবং তাতে তার ভারি মজা কি না এরকম প্রশ্নও আছে। সেরকম কিছু নিষ্পাপ আদর্শবোধ আর মঙ্গলচিন্তাও থাকে। বড় হয়ে যখন রোজগার করব, তখন যারা গরিব তাদের কোনওভাবে সাহায্য করব, বা এমন কিছু করব যাতে দেশের-দশের ভালো হয়। প্রথম যৌবনেও অনেকের ‘এ বিশ্বকে আরো বাসযোগ্য করে যাব’ গোছের একটা আদর্শবোধ কাজ করে, যা সবক্ষেত্রে রাজনৈতিক সক্রিয়তার রূপ না নিলেও, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, কাজের জায়গায় বা সৃজনশীল উদ্যোগে কোনওরকম আপোষ না করার মনোভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আস্তে-আস্তে বড় হয়ে ওঠার সাথে-সাথে অনেক স্বপ্নভঙ্গ হয়, তার সব কিছুই ব্যক্তিগত আশা- আকাঙ্ক্ষার নয় (যেমন, পাইলট, রকস্টার, বা তুখোড় খেলোয়াড় হব)। তার সাথে অভিজ্ঞতার পথের ধুলোয় এক ধরনের বাস্তববাদের আস্তরণ পড়ে আমাদের ভাবনায়, কথায় ও কাজে। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস এবং নানা দায়িত্বের চাপে তারপর আমাদের দৃষ্টিপথ খানিকটা সংকীর্ণ হয়ে যায়। তবে দৈনন্দিন জীবনের হাজারটা চিন্তার তলায় চোরাস্রোতের মতো এই ফেলে আসা কিছু ভাবনাচিন্তা, প্রশ্ন এবং ইচ্ছে মনে থেকে যায়। কখনও-কখনও হঠাৎ যখন তারা ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে, তখন ফিরে দেখতেই হয়।
ভেবে দেখতে গেলে আমাদের জীবনকে শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য এই পর্যায়গুলো দিয়ে ভাগ করা এবং প্রতি পর্যায়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা লক্ষ্য-আকাঙ্ক্ষা-সাধ্য-ক্ষমতা এই সবগুলো আলাদা হবে ভাবাটা একটু যান্ত্রিক। আসলে সবসময়েই আমাদের মধ্যে একাধিক সত্তা বিরাজমান। তাই প্রৌঢ় মানুষের ছেলেমানুষি খেয়াল নিয়ে যেমন হাসা হয়, আবার কিশোরের সুচিন্তিত মতামত পাকামি বলে বর্ণনা করা হয়। আবার জীবনচক্রের অমোঘ আবর্তনে কিছু কিছু ধ্যানধারণা, বিচারধারা, ভালো লাগা পালটে যায়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই বিভিন্ন সত্তাগুলোর আপেক্ষিক ভূমিকা পালটায়, কিন্তু কোনও সত্তাই একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় না। আমার মনে হয় ‘ফিরে দেখা’-র মধ্যে আমাদের এই বিভিন্ন সত্তার মধ্যে একটা কথোপকথনের প্রক্রিয়াও যুক্ত আছে।
লিখতে বলা হয়েছে কোনও আইডিয়াকে ফিরে দেখা নিয়ে; তাই নিয়ে ভাবতে গিয়ে এইসব চিন্তা মনে এল। ফিরে আমরা অনেক কিছুই দেখি, যেমন পুরনো অ্যালবাম, প্রিয় মানুষ, জায়গা, গান, গল্প, বা ঘটনার স্মৃতি। সেরকম কিছু চিন্তা বা ইচ্ছেও আমরা ফিরে দেখি, তার কিছু অপরিণত মনে হলেও কিছু আবার ঘাড়ে চেপে বসে; তখন সংশয় জাগে, এখন যা ভাবি তাই ঠিক, না আগেই ঠিক ভাবতাম? আসলে এই সংশয়বোধও একটা বয়েসের পরেই আসে। যৌবনে যা ভাবছি, যা করছি, সব কিছু নিয়ে অনেক বেশি নিশ্চয়তা থাকে। অভিজ্ঞতার আরেক নাম হল ভুল থেকে শেখা। আজ যা ভাবছি, কিছুদিন বাদে সেই ভাবনা খানিক পালটে যেতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা সম্পর্কে সচেতন থাকা। তাই কোনও আইডিয়াকে ফিরে দেখা যেন এক বহমান আলোচনাসভা, যার কোনও বাঁধা রুটিন নেই, যেখানে আমাদের বিভিন্ন সত্তার মধ্যে কথোপকথন চলতে থাকে, পরিবর্তনশীল দুনিয়া যেখানে নিত্যনতুন প্রশ্ন তোলে, দ্বন্দ্বের মুখোমুখি ফেলে ।
এখন আইডিয়া কথাটি অনেক অর্থে ব্যবহার করা হয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল মনশ্ছবি— অর্থাৎ আমাদের মনের জগতে যা ছবির মতো বিরাজ করে। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগে আমরা প্রধানত যে যে অর্থে কথাটা ব্যবহার করি, তার একটা হল বাস্তব-পৃথিবীতে কী থেকে কী হয় সেই নিয়ে আমাদের ভাবনা বা ধারণা বা অনুমান, আরেকটা হল কোনও বিষয় নিয়ে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান (‘তোমার কোনও আইডিয়া নেই’)। আবার কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে কোনও কৌশল বা উপায় অর্থেও কথাটা ব্যবহার হয় (যেমন, একটা গল্পের বা গবেষণার আইডিয়া, কোনও কাজ হাসিল করার আইডিয়া)। আমাদের মনের মধ্যে যে নানা চিন্তা আসে, তার সবই আইডিয়া নয়; তার কিছু অনুভূতি, সংবেদন, বা আবেগ। আইডিয়া শব্দটার প্রচলিত প্রয়োগের মধ্যে তাই বাইরের জগৎ সম্পর্কে একটা ধারণা এবং তা ব্যবহার করে কোনও কিছু করার পরিকল্পনা— এই দুটো ব্যাপার সচরাচর জড়িয়ে থাকে।
আবার আইডিয়ার সাথে আইডিয়াল কথাটিরও সম্পর্ক আছে। কোনও কিছুর আদর্শ বা নিখুঁত রূপ নিয়ে আমাদের যে মনোগত ধারণা, সে কোনও মানুষ বা জিনিসের গুণ সম্পর্কে হতে পারে, আবার কোনও প্রক্রিয়া (process), পরিবেশ (conditions) বা ব্যবস্থা ( system) সম্পর্কেও হতে পারে। তার মানে যা হয়, যেভাবে হয়, তা হল আইডিয়ার ঘরে, আর যা হলে বা যেভাবে হলে সর্বোত্তম হয়, তা হল আইডিয়ালের ঘরে। আইডিয়ালিস্ট বা আদর্শবাদী হলেন তিনি, যিনি হয় কোনও ব্যক্তিগত আচরণে নীতিনিষ্ঠ (যেমন, সততা, পরোপকারিতা) বা বৃহত্তর পরিসরে উন্নতিসাধনের জন্যে কোনও কল্যাণকামী প্রয়াসের সাথে যুক্ত (যেমন, রাজনীতি বা সমাজসেবা) । আইডিওলজি বা মতাদর্শ কথাটি এসেছে আইডিয়া আর আইডিয়াল এই দুটি ধারণা মিশে— তা হল সমাজ, রাজনৈতিক বা অর্থব্যবস্থার চালিকাশক্তিগুলো সম্পর্কে ধারণা এবং আদর্শ ব্যবস্থা কী হওয়া উচিত এই নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা। আদর্শ ব্যবস্থার সমালোচনা হিসেবে অনেক সময়ে তাকে কল্পলোকীয় (utopian) বলে উল্লেখ করা হয়।
ফিরে আমরা অনেক কিছুই দেখি, যেমন পুরনো অ্যালবাম, প্রিয় মানুষ, জায়গা, গান, গল্প, বা ঘটনার স্মৃতি। সেরকম কিছু চিন্তা বা ইচ্ছেও আমরা ফিরে দেখি, তার কিছু অপরিণত মনে হলেও কিছু আবার ঘাড়ে চেপে বসে; তখন সংশয় জাগে, এখন যা ভাবি তাই ঠিক, না আগেই ঠিক ভাবতাম?
এই লেখাটি লিখতে বসে ভাবছিলাম, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ফিরে দেখেছি এমন আইডিয়া অনেকই আছে, কিন্তু যে-চিন্তাটা ঘুরে ফিরে বার বার এসেছে এবং আবার আসবেও জানি, যার সাথে অর্থনীতিতে আমার নিজের গবেষণারও যোগ আছে, তা হল : অসাম্য কি মানবসমাজে অনিবার্য ও অবধারিত একটি সমস্যা, না কি এর সমাধান সম্ভব? প্রথম যৌবনে মনে হত এর সমাধান অবশ্যই সম্ভব এবং তার জন্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বব ডিলানের গানের কথার মতো, ‘Ah, but I was so much older then I’m younger than that now’, অর্থাৎ, তারুণ্য হল নিঃসংশয় প্রত্যয়ের বয়েস, আর অভিজ্ঞতার সাথে আসে সংশয় বা এক ধরনের অজ্ঞেয়বাদ। আসলে জানা ও বোঝার একটা বড় অঙ্গ হল যে, কী জানি না আর কী বুঝি না সেটা বোঝা। অসাম্য ধারণাটি এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে পরবর্তীকালে একাধিকবার ফিরে দেখেছি। চিন্তাভাবনার এই পথপরিক্রমায় আগের দেখাগুলো একেবারে ভুল ছিল তা মনে হয়নি, কিন্তু দৃষ্টিকোণ পালটাতে থেকেছে। আসলে হয়তো পথ যদি সরলরেখার মতো না হয় এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যবিন্দু না থাকে, এটাই স্বাভাবিক।
২.
অসাম্য কী? মানুষে-মানুষে অনেক তফাত আছে, তা তাদের চেহারা, গুণ বা স্বভাবে— এমনকী যমজ ভাইবোনেদের মধ্যেও থাকে। আর শুধু মানুষই বা কেন, প্রকৃতিতে– সে জীবজগতেই হোক বা জড়বস্তুই হোক– একদম একরকম দুটো নমুনা পাওয়া মুশকিল। ভিন্নতা কি অসাম্য? সেটা তখনই হয়, যখন মানবসমাজ কিছু গুণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক মূল্যায়ন আরোপ করে এবং সেই গুণটি বেশি বা কম থাকা সেই মানুষ বা বস্তুর সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থানের তফাত করে দেয়। উদাহরণ হিসেবে জড়বস্তুর ক্ষেত্রে ভাবা যায় হিরে আর কয়লা, উর্বর জমি আর অনুর্বর জমি, আর মানুষের গুণের ক্ষেত্রে বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি, রূপ বা বিশেষ কোনও গুণ (যেমন গানের গলা), অথবা পারিবারিক পরিবেশ (আর্থিক, শিক্ষাগত, সামাজিক পরিচিতি) এগুলো ভাবা যেতে পারে। এখানেও আবার আইডিয়া আর আইডিয়ালের সম্পর্ক এসে যাচ্ছে— কোনও গুণের সর্বোত্তম (এবং সর্বনিম্ন) মাত্রা সম্পর্কে ধারণা থাকলে পরেই তার মূল্যায়নে কোনও মাপকাঠি ব্যবহার করা যায়।
আবার এই যে বিভিন্ন গুণের যে-মূল্যায়ন এবং তার জন্যে যে-প্রাপ্তি (সে অর্থই হোক বা সম্মান বা ক্ষমতা), তা আবার সময়ের সাথে পালটায়। খুব ভাল তরোয়াল চালাতে পারা এক সময়ে খুব মূল্যবান গুণ ছিল, এখন আর নেই; আবার কম্পিউটারে কোডিং করার দক্ষতা এখন যতটা মূল্যবান, কয়েক দশক আগেই তা ছিল না।
এই যে মানুষে-মানুষে বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যে যে পার্থক্য, তার আর্থিক বা সামাজিক পরিণাম যদি আলাদা হয়, তাহলে সেটাও তো অসাম্য বা একভাবে দেখলে বৈষম্য। অথচ, এর অনেকগুলো নিয়েই প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার নেই। মেধা, দক্ষতা এবং পরিশ্রমের ফল কেউ পেলে এবং সেই কারণে অসাম্য তৈরি হলে সেখানে আপাতদৃষ্টিতে নীতিগত কারণে আপত্তি করার কিছু থাকে না।
তাই এখানে প্রশ্ন তুলতে হয়, প্রতিভা বা দক্ষতা বিকাশের সুযোগের অসাম্য নিয়ে, এবং সেই নিয়ে সত্যি দ্বিমত হবার অবকাশ নেই। দারিদ্র্য, শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে আর্থিক বা সামাজিক উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে এমন উদাহরণ চারপাশে অজস্র। বামপন্থী মতধারায় এই ধরনের অসাম্যের ওপরেই জোর দেওয়া হয়।
আমি আর্থিক সুযোগের অসাম্য নিয়েই মূলত আলোচনা করলেও, সুযোগের অসাম্যেরও আরও অনেক উদাহরণ আছে— যেমন, লিঙ্গ বা জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের কারণেও প্রতিভা বা দক্ষতার দিক থেকে একদম সমান দুজন মানুষ সমান সুযোগ পায় না এবং তাই সময়ের সাথে তাদের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থানেও বড় ফারাক এসে যায়।
অসাম্যের এই দিকটি একাধিক কারণে সমস্যাজনক।
এক তো একটি মানুষের সম্ভাবনা ও বাস্তবের মধ্যে বড় ফারাকের মধ্যে একটা মানবিক ট্র্যাজেডির দিক আছে : ‘এমন মানবজমিন রইল পতিত/ আবাদ করলে ফলতো সোনা’। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবার পরের ছুটিতে আমি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটি দরিদ্র এলাকার কিছু বাচ্চাকে পড়াতে গিয়ে এটা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি। এই সাত-আট বছরের বাচ্চাগুলোর মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও উৎসাহী, তাদের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে বাড়ি ফিরে খুব মন খারাপ হয়ে থাকত। বুঝতাম তারা কেউ তাদের সম্ভাবনা পূরণ করার ধারে-কাছে যেতে পারবে না দারিদ্র্যের (এবং তাদের মধ্যে মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক নানা বেড়াজালের) কারণে। অথচ এরাই যদি আমার নিজস্ব সামাজিক বৃত্তে জন্মাত ও বড় হত, তাহলে পরিণাম অনেকটাই আলাদা হত।
এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি প্রথম অসাম্য নিয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভাবা শুরু করলাম। কলেজজীবনে বাম রাজনীতির দিকে ঝোঁকের পেছনেও সেই পড়ানোর অভিজ্ঞতার একটা ভূমিকা ছিল।
একজন মানুষের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি বাদ দিয়েও, বৃহত্তর সামাজিক স্তরে নীতিগত ভাবে অসাম্য কী কারণে সমস্যাজনক ভাবতে গিয়ে মনে হল, সমান গুণসম্পন্ন দুটি মানুষের সুযোগের বৈষম্যের জন্যে অর্থনৈতিক সাফল্য (এবং তার সাথে সামাজিক মর্যাদা) ভীষণ আলাদা হলে মেধাতন্ত্রের যে মূল যুক্তি, যোগ্যতার সম্মান, সেটাই খাটে না।
শুধু তাই নয়, কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়া শুরু করার ফলে তখন সদ্য উৎপাদনশীলতার যুক্তির সাথে পরিচয় হয়েছে। কোনও দেশের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার একটি প্রধান শর্ত হল সম্পদের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন ও নিয়োগ। তার মধ্যে শ্রম আছে, পুঁজি আছে, প্রযুক্তি আছে, প্রাকৃতিক সম্পদ আছে— এগুলো যে ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল, সেখানে নিয়োজিত হলেই জাতীয় আয় সর্বাধিক হবে। সাধারণত এই যুক্তি বাজারব্যবস্থার স্বপক্ষে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়— যেমন সরকারি ক্ষেত্রে আয় আর দক্ষতা, উদ্যম, বা পরিশ্রমের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ হওয়া। কিন্তু এই উৎপাদনশীলতার যুক্তিতেই দারিদ্র্যের ফলে বাজারব্যবস্থাতেও মানবসম্পদের বিকাশের অভাবে প্রতিভা ও দক্ষতার যে অপচয় হয় (যেমন, যে বৈজ্ঞানিক বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত, সে গাড়ির মেকানিক হল, যাতে ক্ষতি শুধু তার নয়, বৃহত্তর সমাজেরও) মূলধারার অর্থনীতির পাঠ্যবইয়ে সেই আলোচনার অভাব অস্বস্তিকর লাগছিল (তখনও আধুনিক উন্নয়নের অর্থনীতির সাথে বেশি পরিচয় হয়নি, যেখানে অমর্ত্য সেন থেকে থিওডোর শুল্ট্সের এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রভাব ছড়াতে শুরু করেছে, যা নিয়ে পরে গবেষণার জগতে ঢুকে আমি নিজেও কাজ করব)।
বাম রাজনীতির প্রতি ঝোঁক ছিল এই ধরণের সমস্যাগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে, কিন্তু এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান কী, তার উত্তরে ‘সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইসব সমস্যা থাকবে না’ ধরনের বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ছাড়া খুব কিছু পেতাম না। কিন্তু আমার কলেজজীবন চলাকালীনই আশির দশকের শেষে বিশ্বরাজনীতিতে অনেক পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনে সমাজতন্ত্রের যে-মডেলটা ছিল, সেটা যে অর্থনৈতিক ভাবে কার্যকর হয়নি শুধু তা নয়, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক থেকে দেখলেও সেগুলোকে সমর্থন করা খুব শক্ত, আরও অনেকের মতো আমারও এই উপলব্ধি হতে শুরু করেছে, মনে হতে শুরু করেছে অসাম্যের বিশ্লেষণ এবং তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজতে হবে ‘হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্খানে’।
কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে মূলধারার অর্থনীতি পড়তে গিয়ে অসাম্য নিয়ে নতুন কিছু আইডিয়ার সাথে পরিচয় হচ্ছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে ফিরে দেখে আমার আগের চিন্তাগুলো বেশ অপরিণত মনে হতে লাগছিল। সুযোগের অসাম্য যে কোনওভাবেই কাম্য নয়, সেই চিন্তাটা পালটায়নি, কিন্তু এই পরের পর্যায়ে অসাম্য নিয়ে নতুন কিছু চিন্তা মাথায় এল।
একটা চিন্তা হল, অসাম্য নিয়ে প্রধান সমস্যা কি দারিদ্র্য এবং বঞ্চনা (deprivation) নিয়ে, না কি ধনীদের ধনী হওয়া নিয়ে? যে-সমাজে কেউ দরিদ্র নন, এবং সুযোগের এক ধরনের সাম্য বিরাজমান (উদাহরণ হিসেবে সুইডেন বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্যান্য দেশের কথা ভাবা যেতে পারে) সেখানে কেউ ন্যায়সঙ্গত পথে অর্জন করে ধনী এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, তা নিয়ে নৈতিক আপত্তি কি হতে পারে? সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনে তোলা প্রশ্ন, ‘বলতে পার বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?/ গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?’ খুবই সঙ্গত। গরিবের গাড়ি চাপা পড়াটা অবশ্যই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বড়মানুষ কাউকে চাপা না দিয়ে মোটর চড়লে সমস্যাটা কী?
এখন বড়লোকেদের সম্পদের উৎস অনেক সময়েই অন্যায় পথে হয় (যেমন, গরিবের জমি দখল করে) এবং সেখানে সম্পদের পুনর্বণ্টনের পক্ষে একটা নৈতিক যুক্তি আছে। কিন্তু এও তো সত্যি যে, পরিশ্রম-উদ্যম-সঞ্চয়-বিনিয়োগ এই প্রক্রিয়াতেও অনেকে ধনবান হন, এবং তারা যদি কর দেন এবং আইন মেনে চলেন, তাতে নৈতিক আপত্তির কী থাকতে পারে? আমাদের নৈতিক সমস্যা যদি দারিদ্র্য ও বঞ্চনা হয় তাহলে তার সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থসমাগমের জন্যে ধনীদের ওপর কর আরোপ করা সমর্থনীয়, কিন্তু সেটা একটা ব্যবহারিক যুক্তি, ধনী-দরিদ্রের ফারাক নির্মূল করে দেওয়ার যুক্তি নয়।
না কি অসাম্য নিয়ে সমস্যাটা শুধু দারিদ্র্য বা বঞ্চনা নয়, জীবনযাত্রার আপেক্ষিক মান নিয়েও? এই অনুভূতিটা ‘চন্দ্রবিন্দু’-র ‘খেলছে শচীন’ গানটির কিছু লাইনে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, যেমন ‘আমরা খাব মুড়কি মুড়ি/ তোমরা চিকেন চাউ’ এবং ‘আর তোমরা যাকে করছ বিয়ে/ আমিও তাকে চাই’। এই ধরনের অসাম্য কি কখনওই নির্মূল করা সম্ভব? আরও বড় কথা হল, এই ধরনের অসাম্য নির্মূল করার স্বপক্ষে কি কোনো নৈতিক যুক্তি আছে? মার্কিন কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্ট ভনেগাটের ‘হ্যারিসন বার্গেরন’ গল্পে ভবিষ্যতের এমন এক সমাজের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেখানে কেউ অন্য কারোর থেকে বুদ্ধি, রূপে, বা শারীরিক ক্ষমতায় বেশি হতে পারবে না। এই নীতি বলবৎ করতে যারা যত বেশি বুদ্ধিমান তাদের কানে তত জোরে রেডিয়োর আওয়াজ শোনানো হবে যাতে তারা বেশি ভাবতে না পারে, যারা রূপবান মুখোশ পরে তাদের মুখ ঢাকতে হবে, এবং যারা বলবান তাদের ভারী ওজন বইতে হবে যাতে তারা অন্যদের থেকে কোনও বাড়তি সুবিধা না পায়। সুযোগের সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া এক ব্যাপার, আর এরকম হাতুড়ি চালিয়ে মানুষে-মানুষে সব প্রভেদ মুছে দেবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ আরেক ব্যাপার, যার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া মুশকিল।
এও তো সত্যি যে, পরিশ্রম-উদ্যম-সঞ্চয়-বিনিয়োগ এই প্রক্রিয়াতেও অনেকে ধনবান হন, এবং তারা যদি কর দেন এবং আইন মেনে চলেন, তাতে নৈতিক আপত্তির কী থাকতে পারে? আমাদের নৈতিক সমস্যা যদি দারিদ্র্য ও বঞ্চনা হয় তাহলে তার সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থসমাগমের জন্যে ধনীদের ওপর কর আরোপ করা সমর্থনীয়, কিন্তু সেটা একটা ব্যবহারিক যুক্তি, ধনী-দরিদ্রের ফারাক নির্মূল করে দেওয়ার যুক্তি নয়।
এই পর্যায়ে অসাম্য নিয়ে আমার চিন্তায় আরেকটি বড় প্রশ্ন ছিল, আয়ের অসাম্য যদি জাদুবলে ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভবও হয়, কাজ করার বৈষয়িক প্রণোদনার অভাবে মানুষ কাজ করার উৎসাহ পাবে কি? আর তা না হলে সার্বিক উৎপাদনশীলতা নিম্নগামী হতে বাধ্য। তাতে অসাম্য ঘুচলেও সবারই জীবনযাত্রার মান কমবে, যদিও হয়তো চরম দারিদ্র্য থাকবে না। তার থেকে খানিক অসাম্য যদি বৈষয়িক প্রণোদনার জন্যে আবশ্যক হয়, তাহলে দরিদ্রশ্রেণির লোকেরাও তাতে লাভবান হতে পারেন, যদি ধনীদের উদ্বৃত্ত বিত্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে শ্রমের চাহিদা বাড়ায়, এবং করব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বাড়ে। বৈষয়িক প্রণোদনার অভাবে কী হতে পারে তা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা চালু রসিকতা ছিল : এক শ্রমিক আরেকজনকে বলছে, ‘ওরা আমাদের মাইনে দেওয়ার ভান করে, আর আমরা কাজ করার ভান করি!’ এখন কেউ ভাবতে পারেন যে, নতুন সমাজব্যবস্থায় মানুষের মানসিকতা পালটে গেলে প্রণোদনা ছাড়াই মানুষ কাজ করবে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে তার ভিত্তিতে বিকল্প অর্থব্যবস্থার কথা ভাবা মুশকিল।
অসাম্য ও তার সমাধান নিয়ে তাই এই পর্যায়ে আমার চিন্তাভাবনা দুটো পরস্পরসম্পর্কিত খাতে বইছিল। একটা হল প্রগতিশীল (progressive) করব্যবস্থার গুরুত্ব, যাতে ধনীরা ক্রমবর্ধমান হারে কর দেবেন, এবং তা শুধু আয়ের ওপরে নয়, কোম্পানির লাভ, স্টক মার্কেটে লাভ, এবং সম্পদের ওপরেও ধার্য হবে। আর অন্যটা হল, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়া, যার ফলে খানিকটা হলেও সুযোগের অসাম্যের সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে, যার উদাহরণ হিসেবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর কথা ভাবা যায়। এখন করের হার যত বেশি হবে, ব্যক্তিগত উদ্যম ততই ব্যাহত হবে (সে কাজ করারই হোক বা সঞ্চয় বা বিনিয়োগেরই হোক) তাই এখানেও কতটা পুনর্বণ্টন সম্ভব সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু তা হল কৌশলগত প্রশ্ন, যার উত্তর স্থান-কাল ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে, নীতিগত প্রশ্ন নয়।
বহুদিন আমার চিন্তাভাবনা এই ধারায় বইছিল, কিন্তু সম্প্রতি আবার এই আইডিয়া নিয়ে ফিরে দেখছি।
৩.
ইদানীং অসাম্য নিয়ে যে-চিন্তাটা মাথায় ঘুরছে তা হল, অর্থনৈতিক অসাম্যের চালিকাশক্তিগুলো তো শুধুই অর্থনৈতিক নয়, সেখানে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আরও অনেক উপাদান কাজ করে। তাই কৌশল হিসেবে শুধু অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টনের কথা ভাবলেই কি চলবে? ধরুন, এই মুহূর্তে জাদুবলে সবার আয় বা সম্পদ সমান করে দেওয়া হল। সেই অবস্থা থেকে শুরু করে প্রগতিশীল করব্যবস্থা এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নানা নীতিও চালু করে দেওয়া হল। তাহলেও কি সময়ের সাথে-সাথে অসাম্য ক্রমশ আবার ফিরে আসবে না? তার কারণ, অসাম্যের শিকড়ের বিস্তার অর্থনীতির অনেক গভীরে। পারিবারিক পটভূমি ও পরিচিতি, সামাজিক বৃত্ত, প্রভাবশালী মহলে যোগাযোগ, এ সব কিছুরও বড় ভূমিকা আছে। একই প্রতিভার দুজন মানুষের পেশাগত সাফল্য শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরে নির্ভর করে না— তাঁরা বাড়িতে কী পরিবেশে বড় হয়েছেন, তাঁদের সামাজিক পরিচিতির বৃত্তটি কী, কোন পারিবারিক যোগাযোগ কোন পর্যায়ে কীভাবে তাঁদের সাহায্য করে এরকম অনেক উপাদান কাজ করে, যা শুধু মেধা বা অর্থনৈতিক সামর্থ্য এই ছক দিয়ে ধরা যায় না।
একদিক থেকে দেখলে এটা খুব সোজা কথা— যদি সরকারি চাকরি, বাস বা পেট্রল পাম্পের লাইসেন্স থেকে শুরু করে জমি, প্রাকৃতিক সম্পদের দখলদারি, পরিকাঠামোর বিকাশ ও পরিচালন, সরকারি আইনকানুন বা প্রশাসনের প্রয়োগ সব কিছুতেই রাজনৈতিক যোগাযোগ একটা বড় ভূমিকা নেয়, তাহলে সেই সূত্রে যে সুযোগের অসাম্য তৈরি হবে, তার প্রভাব অর্থনৈতিক অসাম্যের ওপর পড়তে বাধ্য। আবার অর্থনৈতিক অসাম্য সামাজিক অবস্থান এবং প্রভাবের অসাম্যকে বাড়াবে। এদের মধ্যে সম্পর্কটা দু-দিকেই কাজ করে এবং একটা আরেকটাকে বাড়ায়।
তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতে এই প্রক্রিয়াগুলোর ওপরে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনকানুনের কিছু বাধাবন্ধন থাকে, কিন্তু তাহলেও কোনও নীতি দিয়ে সামাজিক ক্ষমতা বা প্রভাবকে পুরোপুরি ঠেকানো যায় না, অনেক সূক্ষ্মভাবে প্রভাব ও ক্ষমতার অসাম্য জীবনের প্রত্যেকটা পরিসরে ছায়া ফেলে। যেমন, হার্ভার্ড বা প্রিন্সটনের মতো আমেরিকার অভিজাত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১০-২৫% আসন দেওয়া হয় উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে, অর্থাৎ প্রভাবশালী পরিবারের আসনপ্রার্থীদের, যাদের ‘legacy applicants’ বলা হয়।
আর শুধু তাই নয়, সরকার অসাম্য বা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যে কল্যাণমূলক নীতিই অবলম্বন করুক, তার বাস্তব প্রয়োগ এই সামাজিক অসাম্যের উপাদানগুলোর ওপর নির্ভর করে; কারণ রাজনীতি, রাষ্ট্রযন্ত্র, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সব কিছুর মধ্যেই সামাজিকভাবেই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর লোকেরা ঢুকে বসে আছে। এই সমস্যাটা সব পরিসরেই বিরাজমান, এবং কোনও ব্যবস্থাই– সে ধনতন্ত্র হোক বা সমাজতন্ত্র– এর থেকে মুক্ত নয়। তথাকথিত সামজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেহেতু সরকার, রাষ্ট্রযন্ত্র, এবং পার্টির প্রভাব অপরিসীম, সেখানে এই সমস্যাটা সর্বক্ষেত্রে বিরাজ করত, এমনকী ব্যক্তিগত ভোগদ্রব্যের বণ্টনেও।
‘অসাম্য’ আইডিয়াটি নিয়ে ফিরে দেখার এই পর্যায়ে আমার চিন্তাভাবনা তাই খানিকটা পালটেছে।
দারিদ্র বা বঞ্চনার ক্ষেত্রে সবার জন্যে জীবনযাত্রা এবং সুযোগের একটা ন্যূনতম মান (absolute level) লক্ষ্য করে এগোনো যায়। আর, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাথে সমান হারে না হলেও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণির সবাই উপকৃত হতে পারেন, তাই খেলাটা আবশ্যকভাবে শূন্য অঙ্কের নয়। কিন্তু ক্ষমতা ও প্রভাবের ক্ষেত্রে অসাম্যের আপেক্ষিক (relative) দিকটা এসে যেতে বাধ্য। এই ক্ষেত্রে অন্য কারোর বাড়তি সুবিধে মানেই আপনার অসুবিধে, অর্থাৎ খেলাটা শূন্য অঙ্কের। অসাম্যের এই দিকটার মোকাবিলা করতে শুধু করব্যবস্থা বা পুনর্বণ্টনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। যে-প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে ছোটো-বড়ো সব পরিসরে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানই হোক বা রাষ্ট্রযন্ত্রই হোক, সেই প্রক্রিয়াগুলোর স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার ওপর নজর দিতে হবে; যেমন আমাদের দেশে দুই দশক আগে তথ্যের অধিকার নিয়ে আইনের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছিল। ঠিকই, এগুলোর কার্যকারিতা সার্বিক রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। এই মুহূর্তে এই ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া শক্ত হলেও, এগুলো নিয়ে সচেতনতা আবশ্যক।
অসাম্য আইডিয়াটা নিয়ে আবার পরে ফিরে দেখলে নিশ্চয়ই আবার খানিকটা নতুনভাবে ভাবব। ফিরে দেখার মানেই তো তাই!
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র