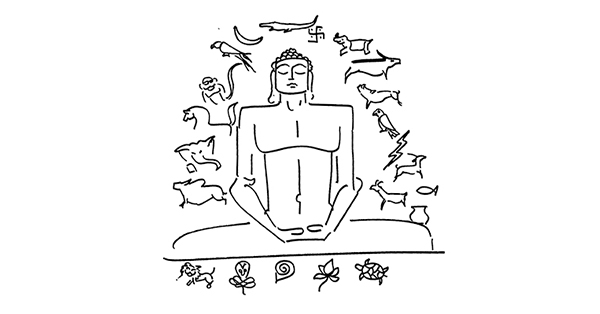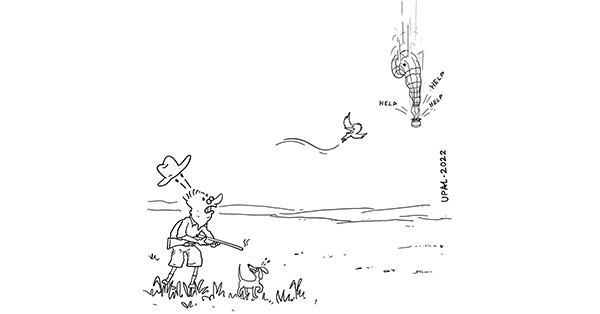যুক্তির বাইরে দাঁড়িয়ে

 কবীর চট্টোপাধ্যায় (December 24, 2022)
কবীর চট্টোপাধ্যায় (December 24, 2022)নব্বই প্লাস তিরিশ; একশো কুড়ি মিনিট খেলা। তারপর কিছু নিখুঁত পেনাল্টি, একটা মিস, একটা অনবদ্য সেভ। তারপর এগারোজন অচেনা মানুষের বিশ্বজয় দেখে ষোলো হাজার কিলোমিটার দূরের একটা শহরে লাখ-লাখ মানুষের উল্লাস, আনন্দ, ভালবাসা। ওই লোকগুলো হয়তো জানেও না কলকাতা বলে একটা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ওদের দেশের পতাকা ওড়ে; কিন্তু আমরা ওদের জন্য রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি, চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করে ঝগড়া করেছি বিপক্ষের সমর্থকদের সঙ্গে। ‘মানুষ মূলত র্যাশনাল বা যুক্তিবাদী জীব’, অ্যারিস্টটলের এই উক্তিকে যে এইভাবে আমরা ভুল প্রমাণ করে দেব, তা কি তিনি জানতেন?
কেন এই আনন্দ? আর্জেন্টিনা জিতলে কলকাতায় বা ঢাকায় বা জলপাইগুড়িতে বা চট্টগ্রামে লাখ-লাখ মানুষ এইভাবে আনন্দ পাই কেন? কেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ওদের জাতীয় দলের যাত্রা মনোযোগ দিয়ে ফলো করি? জানা সম্ভব নয়। কারণ ভালবাসার কোনও বিশেষ কারণ থাকে না। অধ্যাপক টেরি ইগলটন একবার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মনে করুন আপনি একজনকে ভালবাসেন, এবং যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চান কেন বাসেন। আপনি একটি কাগজে সেই মানুষটির সমস্ত গুণ, সমস্ত ভাল অভ্যেসের কথা এক-এক করে লিখুন। এক নম্বর, সে দয়াপরায়ণ এবং নৈতিক মানুষ। দু’নম্বর, তার রসবোধ অতুলনীয়। তিন নম্বর, তাকে দেখতে আপনার সুন্দর লাগে ইত্যাদি। কিন্তু এবার সেই তালিকা অনুযায়ী আমি যদি সম্পূর্ণ অচেনা একজন লোককে ধরে আনি, যার মধ্যে ওই প্রত্যেকটি গুণই বর্তমান, আপনি কি সেই মুহূর্তেই তারও প্রেমে পড়ে যাবেন? পড়বেন না। অথচ ভালবাসা যৌক্তিক হলে পড়ারই কথা ছিল।
তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যৌক্তিক বিচারেরও পরে কাউকে ভালবাসতে একটা বাড়তি কিছু লাগে। তাকে কেউ বলবেন মনের মিল, কেউ বলবেন ম্যাজিক, কেউ কিছুই বলবেন না। মূল কথা হচ্ছে, তাকে ঠিক বোঝা যায় না। সে নড়েচড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না।
আর্জেন্টিনার প্রতি বাঙালির ভালবাসাটাও তেমনই। খানিক ম্যাজিক, খানিক নেশা।
‘আমরা’ বলছি কেন? আমি কি আর্জেন্টিনার নাগরিক? তা নই, ঠিকই ধরেছেন। তবে কি জানেন, ভালবাসা যেহেতু অযৌক্তিক, সেহেতু সে রাষ্ট্রীয় পরিচিতি বা দেশজ শিকড়ের ধার ধারে না। যার যেথা মজে মন। আসলে নাগরিকত্ব বা পাসপোর্টের চেয়েও অনেক দামি একটা যোগসূত্র আছে, সংস্কৃতির যোগসূত্র। আর্জেন্টিনার ফুটবল-দলকে সাত বছর বয়স থেকে যে-উত্তেজনা, যে-ভালবাসা নিয়ে আমার ফলো করা, সেই ফুটবল-সংস্কৃতিই আমাকে শিখিয়েছে, কীভাবে উজার করে ভালবাসতে হয়। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয় মানে একটা গোটা প্রজন্মের বিশ্বজয়। একটা গোটা প্রজন্মের ফ্যানবেসের দিনের পর দিন দুঃখ, হতাশা, অপমান, রাগ, অভিমান সহ্য করেও ভালবাসা টিকিয়ে রাখার বিশ্বজয়।
১৯৯৮ সালে এই টিমটার প্রেমে পড়ি গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতার খেলা দেখে। লম্বা চুল, কাটালো চেহারা, মধ্যগগনের সূর্যের মতো উজ্জ্বল দুটো চোখ। পেনাল্টিবক্সের আশেপাশে যে-কোনও জায়গা থেকে গোলে বল ঢুকিয়ে দিতে পারেন অর্জুনের নিশানায়। সেবার অবশ্য বিশ্বকাপে বেশিদূর যায়নি আর্জেন্টিনা, নক-আউটে ডাচদের কাছে হেরে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়। কিন্তু ততক্ষণে যে প্রেমে পড়ে গেছি, তার থেকে নিস্তার নেই। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে বেশির ভাগই ব্রাজিল সমর্থক, তাদের চক্রব্যূহে অভিমন্যুসম সেই যে আমার লড়াই শুরু হল, আজও সাদা-নীল জার্সির জন্য সেই লড়াই চলছে। প্রবাদপ্রতিম ফরাসি ফুটবলার এরিক ক্যান্টোনা মোক্ষম বলেছিলেন, ‘দেশ পালটানো যায়, ধর্ম পালটানো যায়, নাম পালটানো যায়, এমনকী প্রেমিক-প্রেমিকাও পালটানো যায়। কিন্তু পছন্দের ফুটবল-দল পালটানো যায় না।’
আমরা যারা নব্বইয়ের দশকে জন্মেছি, তারা কেউ আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ তুলতে দেখিনি। মারাদোনাও আমাদের খুবই ছোটবেলায় খেলা ছেড়ে দিয়েছেন, অতএব তাঁকে আমরা চোখে দেখিনি, অনেক গল্প শুনে ‘অল্প অল্প ভালবেসেছি’। অতএব আর্জেন্টিনা সমর্থনের জন্য বার বার বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে আমাদের প্রজন্মকে— অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকিস, মধ্যমানের দল, বাঙালির সীমিত কল্পনায় সৃষ্ট ‘আরজিতিনা’ বা ‘হার্জেন্টিনা’ শব্দগুলো। তার উপর যদি কোনও হতভাগ্য ফুটবল ফ্যান আমার মতো একাধারে আর্জেন্টিনা, ইস্টবেঙ্গল এবং আর্সেনাল ক্লাবের ফ্যান হন, তাহলে তো কথাই নেই। একবিংশের প্রথম চার-পাঁচ বছরের পরে সাফল্য জিনিসটার মুখই আর দেখলাম না। কিন্তু ওই যে বললাম, ভালবাসা অযৌক্তিক এবং সাফল্যের ধার ধারে না। আমার বাবা আমাকে একবার বলেছিলেন, ‘কেউ যদি প্রেমের সম্পর্কে কী পেলাম কী দিলাম, বা কতটা ইনভেস্ট করলাম, এই ধারার কথা বলে, বুঝবি সেটা প্রেম ছিল না। কারণ যে-ভালবাসা পাবার মতো কিছু করতে পারেনি, তাকেই বরং বেশি করে ভালবাসাটা প্রেমের আসল ধর্ম।’ আমার আর্জেন্টিনাও তাই আশায়-দুঃখে-ভালবাসায় আমার বুকের ভিতর রয়ে গেল। একের পর এক ফাইনালে উঠে হারছি, বিপক্ষ এসে মাটি ধরিয়ে দিচ্ছে, তাও। ‘তাও তো কালো ইঁটের ফাঁকে বটপাতাটা জিভ ভেঙচায়/ পাড়ার নেড়ি বাচ্চাটাকে মুখে করে হাঁটতে শেখায়।’
এবং লিওনেল মেসি। যাঁর কথা না বললেই নয়। একজন মানুষ, যিনি ক্লাবস্তরে সব পেয়েছেন, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন প্রায় দু’দশক ধরে, তাঁর কাছে যেন বিশ্বকাপের ওই শেষ খেতাবটুকুই অধরা রয়ে গিয়েছিল। তাঁর জন্যও কি আমরা রাত জাগিনি? জেগেছি, কারণ আমাদের ওই অযৌক্তিক ভালবাসার আধার তিনি নিজেও হয়ে উঠেছিলেন। ১৮ ডিসেম্বরের রাতে যখন গঞ্জালো মোন্টিয়েলের পেনাল্টি গোলে ঢুকছে, তখন অনুধাবন করতে পাক্কা পাঁচ মিনিট লেগেছিল যে আমরা কাপ জিতছি। হাঁ করে বসেছিলাম বন্ধুদের মাঝখানে। চারিদিকে উল্লাস, হট্টগোল, লাফালাফি, গান। মাঝখানে আমি মগজটাকে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, মেসি এবার বিশ্বকাপে চুমু খাবেন। আমরা বিশ্বকাপ জিতে গেছি।
কী বলছেন? ‘আমরা’ বলছি কেন? আমি কি আর্জেন্টিনার নাগরিক? তা নই, ঠিকই ধরেছেন। তবে কি জানেন, ভালবাসা যেহেতু অযৌক্তিক, সেহেতু সে রাষ্ট্রীয় পরিচিতি বা দেশজ শিকড়ের ধার ধারে না। যার যেথা মজে মন। আসলে নাগরিকত্ব বা পাসপোর্টের চেয়েও অনেক দামি একটা যোগসূত্র আছে, সংস্কৃতির যোগসূত্র। আর্জেন্টিনার ফুটবল-দলকে সাত বছর বয়স থেকে যে-উত্তেজনা, যে-ভালবাসা নিয়ে আমার ফলো করা, সেই ফুটবল-সংস্কৃতিই আমাকে শিখিয়েছে, কীভাবে উজার করে ভালবাসতে হয়। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয় মানে একটা গোটা প্রজন্মের বিশ্বজয়। একটা গোটা প্রজন্মের ফ্যানবেসের দিনের পর দিন দুঃখ, হতাশা, অপমান, রাগ, অভিমান সহ্য করেও ভালবাসা টিকিয়ে রাখার বিশ্বজয়।
কারণ ওস্তাদের মার শেষ রাতে। এবং ১৮ ডিসেম্বর ওস্তাদ যা মারলেন, তারপর থেকে পাঁড় নাস্তিক হয়েও মেসির মতোই স্বর্গের দিকে দুই আঙুল তুলে ধন্যবাদ জানাতে কার্পণ্য করছি না।
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook